 |
| আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার |
২৫ জুলাই অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জন্মদিন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার আমাদের একটি বাতিঘর। বাতিঘরের আলোয় গভীর সমুদ্রে পথ হারানো মানুষ পথের দিশা পায়। আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখান মানুষকে।
আলোকিত মানুষ চাই শ্লোগানকে সামনে রেখে যে মানুষটি আলোকিত মানুষ গড়ার ব্রত নিয়েছেন তাঁকে আমরা সবাই চিনি। তিনি আমাদের সবার প্রিয় সায়ীদ স্যার। পুরো নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। 'আলোকিত মানুষ চাই' আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে সত্তরের দশকের শেষ পর্বে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।
এই কেন্দ্র পরিচালিত মূলত বই পড়া কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের হাজার হাজার স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও কেন্দ্র পরিচালিত আরো নানারকম সামাজিক কাজ দেশে এবং বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় তিনি পথিকৃত্। বিনোদন ও সৃজনশীলতার গুণে টিভি উপস্থাপনাকে তিনি নিয়ে গেছেন মননশীলতার উচ্চতর স্তরে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, জার্নাল অনুবাদসহ সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃজনশীলতা ও মননের পরিচয় রেখেছেন।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ২৫ জুলাই ১৯৩৯ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত কামারগাতি গ্রামে। তাঁর পিতা আযীমউদ্দিন আহমদ ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষক। মায়ের নাম করিমুন্নেসা।
পিতার শিক্ষক হিসেবে অসামান্য সাফল্য ও জনপ্রিয়তা শৈশবেই তাকে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট করে।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৯৫৫ সালে পাবনা জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ
করেন। উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে।
তিনি ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. (অনার্স) ও ১৯৬১ সালে একই
বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
পিতার প্রভাব
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ খুব অল্প বয়সে মাকে হারান। তিনি ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে
তৃতীয়। আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদের জীবনে তাঁর পিতার শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাব
সুস্পষ্ট। পিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষক হিসাবে আব্বা ছিলেন খ্যাতিমান। ১৯৫০ সালে আমি যখন
পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, আব্বা তখন পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কথা উঠলে
এমন সশ্রদ্ধ উদ্বেলতায় উপচে পড়ত যে মনে হত কোনো মানুষ নয়,
কোনো দেবতা নিয়ে তারা কথা বলছে। একজন ভালো শিক্ষক ছাত্রদের
হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভালোবাসার যে কী দুর্লভ বেদিতে অধিষ্ঠিত থাকেন আব্বাকে দেখে তা টের
পেতাম। একজন মানুষের এর চেয়ে বড় আর কী চাওয়ার থাকতে পারে। তখন থেকেই আমি ঠিক
করেছিলাম এই পৃথিবীতে যদি কিছু হতেই হয় তবে তা হবে শিক্ষক হওয়া,
আব্বার মতোন শিক্ষক।
ধন নয় মান নয়, খ্যাতি, বিত্ত
বিছুই নয়,
একজন নাম পরিচয়হীন শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের মাঝখানে জীবন
কাটিয়ে দেবার এই সিদ্ধান্তটি যেসব কারণে ছেলেবেলাতেই নিতে পেরেছিলাম,
আব্বার ব্যক্তিত্বের প্রভাবটাই তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। প্রায়
সব পিতাই চায় তাঁর স্বপ্নের মশালটা নিজের সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে যেতে,
কিন্তু সুযোগ হয় অল্প মানুষেরই। সবার বাবার মত আমার বাবাও
নিশ্চয় চাইতেন তাঁর সন্তানদের মধ্যে এক বা দু'জন তাঁর সাহিত্য ও শিক্ষকতার আদর্শকে উত্তরাধিকার সূত্রে
বহন করুক। শিক্ষক হবার কোনো প্ররোচনা তিনি আমাকে সরাসরি দেননি। আমার ধারণা শিক্ষকতা
আমার রক্তে মিশে ছিল। তাই আমি এভাবে অমোঘ বিধিলিপি মেনে নেয়ার মতো ঐ রাস্তায় চলে
গিয়েছিলাম।'
শিক্ষাজীবন ও
শিক্ষকদের প্রভাব
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ যখন প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন তখন তাঁরা ছিলেন টাঙ্গাইল
থেকে মাইল চারেক দূরে, করটিয়ায়। পাঁচ ছয় বছরের সেই শিশুকে পড়ানোর দায়িত্ব পান শরদিন্দু বাবু। শৈশবের
এই শিক্ষক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এমন, 'আব্বা ছাড়া যে সব মানুষের নিবিড় ও শ্রদ্ধেয় মুখ আমাকে
শিক্ষকতার পথে ডাক দিয়েছিল ছেলেবেলার শিক্ষক শরদিন্দু বাবু তাঁদের একজন। রোজ রোজ
নতুন উপহার দিয়ে স্যার আমাকে পড়ার জগতের ভেতর আটকে রাখতেন। কবে কী উপহার আসবে এই
নিয়ে সারাটা দিন কল্পনায় উত্তেজনায় রঙিন হয়ে থাকতাম। এমনি করে কখন যে একসময় পড়ার
আনন্দ আর উপহার পাওয়ার আনন্দ এক হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। এক সময় অনুভব করেছিলাম
স্যারের আদরের ভেতর থাকতে থাকতে আমি কখন যেন পড়াশুনাকে ভালবেসে ফেলেছি।'
আবদুল্লহ্ আবু সায়ীদের জীবনে তাঁর শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের
প্রভাব বিস্তর। শিক্ষকদের কাছ থেকেই তিনি জীবনকে চিনেছেন,
জগতকে চিনেছেন। তাঁর স্কুল রাধানগর মজুমদার একাডেমি স্কুলের
আর একজন শিক্ষক অমর পালকে তিনি স্মরণ করেছেন এভাবে,'স্যার স্নেহ আর প্রীতি ছাড়া ছাত্রদের কিছুই দিতে জানতেন না।
আমাদের সব দোষ ও লজ্জাকে দুই হাতের আদরে ঢেকে অপর্যাপ্ত প্রীতিতে কেবলই আপ্লুত করে
যেতেন তিনি। সেই স্নেহের ধারা আমার শৈশব থেকে যৌবন পেরিয়ে আজও আমাকে যেন স্নিগ্ধ
করে চলেছে।'
নবম শ্রেণীতে ওঠার পর তিনি রাধানগর মজুমদার একাডেমি ছেড়ে পাবনা জেলা স্কুলে
গিয়ে ভর্তি হন। সেখানে যে সব শিক্ষক তাঁর কিশোর হৃদয়ে স্বপ্ন আর ভালবাসার পৃথিবী
জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্কুলের শিক্ষক মওলানা কসিমউদ্দিন
আহমেদ। স্বপ্নে ভরা চোখ, উদ্দাম জীবনাবেগ, দৃপ্ত, প্রিয়দর্শন
ও আপাদমস্তক আধুনিক কসিম উদ্দিন ছিলেন সারা স্কুলের তারুণ্যের প্রতীক। ক্লাশঘর
থেকে স্কাউটিং, খেলার
মাঠ থেকে বিতর্কসভা সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন ছাত্রদের নেতা ও সহযাত্রী। একাত্তরের
স্বধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন।
১৯৫৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পরের দুই বছর তিনি বাগেরহাট
প্রফু্ল্লচন্দ্র কলেজে পড়েন। কলেজের শিক্ষকদের কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল্লাহ্
আবু সায়ীদ বলেন, 'আমার
জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল শিক্ষকদের দেখা পেয়েছিলাম আমার কলেজ জীবনের দিনগুলোয়।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে গড়া এই কলেজের শিক্ষকদের ভেতর শিক্ষকতার যে
জ্যোতির্ময় রূপ আমি দেখেছি তার সমমানের কোনকিছু আমি আর কখনো কোথাও দেখেছি বলে মনে
পড়ে না।
তিনজন অসাধারণ ইংরেজির অধ্যাপককে পেয়েছিলাম কলেজে। তাঁদের দেখে আমি জেনেছি
শিক্ষকের জীবনঐশ্বর্য কীভাবে একজন ছাত্রকে জীবনের উন্মূখ অনুসন্ধিত্সু ও প্রাথমিক
দিন গুলোয় সারাজীবনের জন্যে তিলে তিলে গড়ে তোলে। এদের কাছে পড়ার পর ছাত্রদের
জীবনকে আলোময় কিছু না দিয়ে কেবল রুটিনমাফিক সিলেবাস শেষ করা আর নোট মুখস্থ করিয়ে
যাওয়াকে আমি আর কখনো শিক্ষকতা বলে ভাবতে পারিনি।' বাংলার অধ্যাপক কালিদাস মুখার্জি,
অর্থনীতির অধ্যাপক নারায়ণ সমাদ্দার এমনি আরো কয়েক জন শিক্ষক
সারাজীবন তাঁর জীবন-প্রেরণার অংশ হয়ে রয়েছেন।
কলেজের স্মৃতিতে আরো একজন তাঁর কাছে চির ভাস্কর, তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে
তিনি বলেন, 'বাগেরহাট
কলেজে আমার একজন নীরব পথপ্রদর্শক ছিলেন তিনি। মূল ভবনটার সামনের দেয়াল ঘেষে
সুদৃশ্য পামগাছের সারি ছিল। এর আঙিনার দরজা দিয়ে ঢুকলেই সিমেন্টের বেদির ওপর
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভাস্কর্যটা চোখের সামনে দেখা যায়।
বিকেলের দিকে যখন কলেজ নির্জন হয়ে আসত, পামগাছ, রেস্তোরাঁ, পুকুর, রাস্তা সবকিছু নিয়ে ক্যাম্পাসটাকে একটা ছোট্ট সুন্দর
রূপকথার দেশের মতো মনে হত, তখন নিঃশব্দে আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সেই ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। তারপর
যিনি একদিন ছিলেন আজ নেই সেই মানুষটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তাঁর ভেতর থেকে
জীবনের দুর্লভ শিক্ষা ও শ্রেয়োবোধকে নিজের ভেতর টেনে নিতে চাইতাম। আমি লক্ষ্য
করতাম বিকেলের সেই স্তব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতর আমার হৃদয় একটা দৃঢ় গভীর
আত্মবিশ্বাসে সুস্থির হয়ে উঠেছে। বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অনেক শিক্ষকের
কাছ থেকেই অনেক দুর্লভ প্রাপ্তি ঘটেছিল যা আমার জীবনকে,
নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই নিঃশব্দ পথপ্রদর্শক
তাঁর জীবনের কর্ম, সাধনা আর একাগ্রতার নিথর শীর্ষ থেকে আমাকে যে নিঃশব্দ নির্দেশ উপহার দিয়েছিলেন
তার সমান আর কিছু ছিল না। আমাদের ছেলেবেলার শিক্ষায়তনগুলোর শিক্ষকদের মান
গড়পড়তাভাবে ছিল যথেষ্ট উন্নত। এ ধরনের শিক্ষকেরা তখন প্রায় সবখানেই ছিলেন। এমন
কিছু মূল্যবোধ সেই শিক্ষকরা ধারণ করতেন যা শ্রেয়জীবনের অনুকুল। আজকের স্কুল-কলেজ
গুলোতে এই মাপের শিক্ষক কমে এসেছে।'
 |
| তদানীন্তন ঢাকা বিশ্ব্বিদ্যাল |
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ বহু প্রথিতযশা শিক্ষকদের সান্নিধ্য
লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজের গুণীজন হিসাবে পরিচিত এসব শিক্ষকরা তাঁর জীবনে
নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন মুনীর চৌধুরী,
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। এসব শিক্ষকদের সম্পর্কে কথা
বলতে গিয়ে এখোনো শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নত হয়ে আসে।
মুনীর চৌধুরীর সাথে আবু সায়ীদের যখন পরিচয় হয় তখন তিনি একজন ভালো শিক্ষক এবং
সেকালের প্রগতিশীল কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে দেশব্যাপী পরিচিত। বাগেরহাট ও পাবনায়
থাকা অবস্থাতেই মুনীর চৌধুরীর আপোষহীন রাজনৈতিক ভূমিকা এবং তাঁর বোন নাদেরা
চৌধুরীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। অবশ্য প্রথম দিনের দর্শনে
মুনির চৌধুরীর নীরব নির্বিকার চেহারা দেখে তিনি কিছুটা যেন হতাশই হয়েছিলেন। এর
কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন রাজনীতি থেকে সরে আসার পর সম্ভবত সংঘাতহীন
নিস্তরঙ্গ জীবন বেছে নেওয়ায় তাঁর চৈতন্য ও বোধের জগত্ থেকে আগের সেই দীপ্তি ও
সজীবতা ঝরে পড়েছিল। মুনির চৌধুরী সম্পর্কে তিনি বলেন,
'মুনীর স্যারের পড়ানো ছিল অনবদ্য।
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়িয়েছিলেন। পড়ানোর প্রাণবন্ত সরস উচ্ছলতার
ভেতর দিয়ে ছোটগল্পের যে নিগূঢ় রস তিনি আমার ভেতর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা আজও আমার মনের
ভেতরকার শিল্পভাবনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে রেখেছে। কিন্তু যে জায়গায় তিনি তাঁর
যুগের সবাইকে অতিক্রম করেছিলেন সেটা হচ্ছে বক্তৃতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাফল্য এসেছিল
এখানেই। তরুণ বয়সে 'কবর'
বা 'মানুষ' এর
মতো নাটক বা রাজনীতির জ্বলজ্বলে সাফল্যের পর আর একবার তাঁর সাফল্য ঝিকিয়ে উঠেছিল
এই জায়গায়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ থেকে শুরু করে অন্তত দুই বছর পর্যন্ত তাঁর
বাচনভঙ্গী আমার নিজের কথা বলার ধরন ধারণকেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিল।'
নানা বিষয় নিয়ে মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর উষ্ণ ও আন্তরঙ্গ
আলোচনা হত। তাঁর শ্রদ্ধেয় মুনীর স্যারের যে গুণ আজও তাঁকে প্রভাবিত করে রেখেছে তা
হচ্ছে তাঁর অপরিসীম উদারতা ও সহৃদয়তা। তিনি আরো বলেন,
'অসামান্য প্রতিভার অধিকারী মুনীর
স্যারের কাছ থেকে আমরা যতটা পেতে পারতাম তাঁর অনেক কিছুই হয়ত আমরা পাইনি আর সেই
দুঃখ আজও আমি ভুলতে পারিনা। কিন্তু তাঁর অনবদ্য শিক্ষকতা,
বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ, অসাধারণ বক্তৃতা প্রতিভা, সুবিপুল মমত্ব, মানবিক দুর্বলতা, ক্ষমা করার অসীম ক্ষমতা, অপরিমেয় গুণগ্রাহিতা ও নাট্যামোদী সদা আনন্দিত হৃদয় এবং
জীবনের প্রতিটি বিষয়ে প্রজ্জ্বলিত নিদ্রাহীন উত্সাহ আমার মনের ওপর গভীর প্রভাব
ফেলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি আমাকে যতটা প্রভাবিত করেছিলেন,
আর কেউ হয়ত ততটা করেননি।'
'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্যারকে শিক্ষক হিসাবে আমরা পাইনি
কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ছাত্র না হলেও আমরা সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্রেরা মনোজগতে সবাই ছিলাম তাঁর ছাত্র।' এভাবেই আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথা বলতে
শুরু করেন। তিনি বলেন, 'অনেক সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সেই সময় বিভিন্ন বিভাগের কর্ণধার হিসাবে অধিষ্ঠিত
থেকে নিজ নিজ বিভাগের মর্যাদাকে লোকশ্রুত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ড. মুহম্মদ
শহীদুল্লাহ্ও ছিলেন বাংলা বিভাগের এমনি এক অধ্যাপক। তাঁর একটি কথা এখনো আমার কানে বাজে।
তিনি বলেছিলেন, আমরা
যে প্রতিদিন ছয় ঘন্টা ঘুমাই, জীবনের প্রেক্ষাপটে এই কথাটার মানে কী?
মানে, প্রতিটা দিনের চার ভাগের একভাগ আমাদের জীবন থেকে বাদ পড়ে
গেল। তাঁকে দু'একবারের
দেখার সুযোগে তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো বড়দিকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ
হয়েছিল। ড. শহীদুল্লাহ ছিলেন আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত। তাঁর মেধা ক্ষুরধার,
অসাধারণ ছিলনা। সাধনা ও শ্রমে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত
করেছিলেন। তিনি সতেরটি ভাষা জানতেন। তাঁর কথা শোনার সবচেয়ে লাভজনক ছিল যে গড়পড়তা
তিন-চার মিনিট পর পরই এমন একেকটা অসাধারণ ও বিস্ময়কর তথ্য তিনি আমাদের শোনাতেন যা
আমাদের অবাক করত।'
বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাঁর তরুণ চেতনাকে প্রায়
পুরোপুরি অধিকার করে নিয়েছিলেন, তিনি অধ্যাপক আহমদ শরীফ। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু
করে আশির দশকের শেষপর্যন্ত যাদেরকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে প্রগতিশীলতা
ও বামপন্থী চিন্তাচেতনা দানা বেঁধেছিল, তিনি তাঁদের একজন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,
'জীবন,
পৃথিবী, প্রেম, সমাজ সবকিছু সম্বন্ধে ক্লাশে তিনি এমন নির্মোহ কঠিন ও
নেতিবাচক কথা বলতেন যা আমাকে আকৃষ্ট ও আতঙ্কিত করে তুলত। আমি তাঁর বাসায় নিয়মিত
যেতাম এবং ভেতরকার উত্কন্ঠার হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা
তর্ক করতাম। তাঁর মধ্যে একটা প্রচন্ড নেতিবাচক মনোভাব কাজ করত। তাঁর নেতিবাচকতার
কাছে আমি ঋণী। কোনো বিষয়ের দিকে ক্ষমাহীন নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকাবার এবং তার
অন্তর্সত্যকে দুঃসাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করার শক্তি আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।'
তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন,
দর্শন বিভাগের প্রধান ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. গোবিন্দ
চন্দ্র দেব, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের
অধ্যাপক ড. হাসান জামান প্রমূখ স্বনামধন্য শিক্ষকদের সাহচর্যে আসার সুযোগ হয়েছিল
তাঁর। স্ব স্ব ক্ষেত্রে মহিমায় ভাস্কর এসব গুণীজনদের সাহচর্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ্
আবু সায়ীদের জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। এই সব মহান শিক্ষকদের দ্বারা
প্রভাবিত হয়েই তিনি এই মহিমান্বিত পেশায় প্রবেশ করেছেন।
বাংলাদেশের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন সমাজসংস্কারক। তিনি মূলত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি ষাট দশকের একজন প্রতিশ্রুতিময় কবি হিসেবে পরিচিত। সে সময় সমালোচক এবং সাহিত্য সম্পাদক হিসাবেও তিনি অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্ফূরণ স্তিমিত হয়ে আসে। তবে আত্মজীবনীসহ নানাবিধ লেখালেখির মধ্য দিয়ে আজো তিনি স্বীয় লেখক পরিচিতি বহাল রেখেছেন। তিনি একজন সুবক্তা। ১৯৭০ দশকে তিনি টিভি উপস্থাপক হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যা ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশে আলোকিত মানুষ তৈরির কাজে নিয়োজিত রয়েছে।
শিক্ষকতা
 |
| ঢাকা কলেজ |
শিক্ষক হিসেবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিংবদন্তিতুল্য। তিনি শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন ১৯৬১ সালে, মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে। পরবর্তীতে তিনি কিছুকাল সিলেট মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬২ সালের পহেলা এপ্রিল তিনি রাজশাহী কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে সরকারি চাকুরিজীবন শুরু করেন। সেখানে পাঁচ মাস শিক্ষকতা করার পর তিনি ঢাকায় ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে যোগ দেন (বর্তমানে সরকারি বিজ্ঞান কলেজ)। এই কলেজে তিনি দু' বছর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেইশ। এরপর তিনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ ঢাকা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জালালউদ্দিন আহমেদের আমন্ত্রনে সেখানে যোগদান করেন। ঢাকা কলেজেই তিনি তাঁর শিক্ষকতা জীবনের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত করেন। সে সময় ঢাকা কলেজ ছিল দেশসেরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলনস্থল। অধ্যাপক আবু সায়ীদ যখন ঢাকা কলেজে যোগ দেন তখন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কথাসাহিত্যিক ও গদ্য লেখক শওকত ওসমান৷ ঢাকা কলেজের শিক্ষকতা জীবন তিনি অত্যন্ত উপভোগ করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ”ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে কলেজে উঠে, অর্থনীতির বইয়ে পড়েছিলাম কেন একজন শিল্পপতি, কন্ট্রাক্টর বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীর চেয়ে একজন শিক্ষকের বেতন কম৷ যুক্তি হিসেবে সেখানে বলা ছিল একজন শিক্ষকের জীবন কাটে মার্জিত”।
তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ঢাকা কলেজে প্রাণবন্ত, সপ্রতিভ, উজ্জ্বল ছাত্রদের পড়ানোর তৃপ্তি, শিক্ষক-জীবনের অনির্বচনীয়তম আস্বাদ ছেড়ে তিনি যেতে চাননি ৷ তাঁর মতে,“বাংলা বিভাগে যোগদান করাটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের ছেড়ে সবচেয়ে খারাপ ছাত্রদের পড়াতে যাওয়ার মত মনে হয়েছে “ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে কলেজে উঠে, অর্থনীতির বইয়ে পড়েছিলেন কেন একজন শিল্পপতি,কন্ট্রাক্টর বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীর চেয়ে একজন শিক্ষকের বেতন কম৷ যুক্তি হিসেবে সেখানে বলা ছিল একজন শিক্ষকের জীবন কাটে মার্জিত,পরিশীলিত পরিবেশে,বৈদগ্ধময় ব্যক্তিদের সাহচর্যে, উচ্চতর জীবনচর্চার অবকাশময় আনন্দে৷ জীবনের সেই মর্যাদা, তৃপ্তি বা শান্তি ঐ ব্যবসায়ী বা নির্বাহীর জীবনে নেই৷ এই বাড়তি প্রাপ্তির মূল্য দিতে শিক্ষকের আয় তাদের তুলনায় হয় কম৷ তাই ঢাকা কলেজের শিক্ষকতায় ঐ তৃপ্তি এত অপরিমেয় হয়েছিল যে কেবল বেতন কম হওয়া নয়, তার জন্য হয়ত বেতন না-থাকাই উচিত হত ৷
অধ্যাপক আবু সায়ীদ কখনোই ক্লাসে রোলকল করতেন না। রোলকলকে তার কাছে মনে হতো সময়ের অপব্যয়৷ তাই বছরের পয়লা ক্লাসেই ঘোষণা করে দিতেন রোলকল না করার ৷ তিনি বলেন “অনিচ্ছুক হৃদয়কে ক্লাশে জোর করে বসিয়ে রেখে কী করব? আমার চ্যালেঞ্জ ছিল এক ধাপ বেশি: কেবল শিক্ষক হওয়া নয়, সব ছাত্রের হৃদয়ের কাছে পৌঁছানো, সব ছাত্রের হৃদয়কে আপ্লুপ করা”। ক্লাশের সেরা ছাত্রটাকে পড়ানোর চেষ্টা করার চেয়ে তিনি পড়াতে চেষ্টা করতেন ক্লাশের সবচেয়ে বোকা ছাত্রটাকে৷ সারাক্ষণ তাকেই বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কেননা তার বোঝা মানে ক্লাসের বাকি সবার বোঝা।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও আবদুল্লাহ
আবু সায়ীদ
তিনি বলতেন চীনা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে “যদি এক বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও তবে শস্য রোপণ কর।যদি ত্রিশ বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও, তবে বৃক্ষ রোপণ কর।যদি এক শ বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও, তবে মানুষ রোপণ কর”।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবগুলো দিক
সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। তিনি অনুভব করেছেন যে
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন অসংখ্য উচ্চায়ত মানুষ। 'আলোকিত মানুষ চাই'- সারা দেশে এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হিসেবে প্রায় তিন দশক ধরে তিনি রয়েছেন
সংগ্রামশীল। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে একটু একটু করে, অনেক দিনে। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে নানা
উথ্থান পতনের মধ্যদিয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছে।
১৯৭৮ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্ম। বিশ্বসাহিত্য
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, এই চিন্তাটি প্রথম আমার মনে জাগে ১৯৬৮ সালের দিকে।
তখনই কিছু মেধাবী এবং প্রতিভাবান তরুণকে নিয়ে আমি একটি ঋদ্ধিধর্মী চক্র গড়ে তোলার
চেষ্টা করি। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাতে ছেদ পড়ে। তারপর স্বাধীনতা আসে।
আমাদের সামনে এক বিপুল সম্ভাবনার জগৎ উন্মেচিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক
সার্বিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেই স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যেতে শুরু করে। কাজেই আবার
নতুন করে আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা শুরু করতে হয়। জাতীয় দুঃখের অর্থপূর্ণ আবাসন এবং
সত্যিকার জাতীয় উন্নতি ক্ষুদ্র মানুষ দিয়ে সম্ভব নয়, এর জন্য চাই বড় মানুষ, আলোকিত মানুষ। এই ভাবনা থেকে আবার ১৯৭৮ সালে আমরা সমবেত
হলাম সেই পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে-তোলার চেষ্টায়- সেইসব মানুষদের, যারা একদিন তাদের যোগ্যতা এবং শক্তি দিয়ে, প্রায়স এবং আত্মদান দিয়ে এই জাতির নিয়তি পরিবর্তন করতে
চেষ্টা করবে।
সব সমাজেই এমন কিছু মানুষ থাকেন সংখ্যায় যাঁরা অল্প; কিন্তু যাঁদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপ্তি, মূল্যবোধের বিকাশ, জীবনের উৎকর্ষ, আত্মমর্যাদার মহিমা- এসবের বড়রকম
বিকাশ ঘটে। এঁরা সেই ধরনের মানুষ যাঁদের কেনা যায় না, বেচা যায় না,
সমাজের তরল স্রোত যাঁদের চারপাশ
দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলে;
কিন্তু যাঁরা এর মাঝখানে থেকেও
প্রবুদ্ধ বৃক্ষের মতো একটা জাতির ভারসাম্য সুস্থিত করে রাখেন। এঁরা তাঁরা - যাঁরা
একটা জাতিকে রক্ষা করেন,
এগিয়ে নেন, জাতিকে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখান। এক কথার বড়মানুষ বলতে যা
বুঝি এঁরা হলেন তাঁরাই। যে কোনো উন্নত জাতির মধ্যে যত স্বল্প সংখ্যাতেই হোক, আমরা এই মানুষদের সন্ধান পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের জাতির মধ্যে এইসব সমৃদ্ধ মানুষের ঐতিহ্য এখনো গড়ে
এঠেনি। আর গড়ে-ওঠার যা-ও বা কিছু সম্ভাবনা ছিল তা-ও এখন কঠিন হয়ে উঠছে।
ইতোমধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নিদারুণ অধঃপতন ঘটেছে, কাজেই আমাদের গতানুগতিকে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর থেকে এই মানুষদের
জন্ম ঘটবে এমন আশা কঠিন। আমাদের পরিবারগুলো উৎকর্ষপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো
গড়ে ওঠেনি। আমাদের সমাজে সেই পরিবার কোথায় যেখান থেকে এই বড়মানুষেরা জন্মগ্রহণ
করবেন? দেশের এই সার্বিক অবক্ষয় এবং
সম্ভাবনাহীনতার ভেতর সীমিত সংখ্যায় হলেও যাতে শিক্ষিত ও উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন
আত্মৎসর্গিত এবং পরিপূর্ণ মানুষ বিকশিত হওয়ার পরিবেশ উপহার দেয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে
চেষ্টা করছি। একজন মানুষ যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন, মূল্যবোধের চর্চা এবং মানবসভ্যতার যা কিছু শ্রেয় ও মহান তার
ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বসম্পন্ন হয়ে বেড়ে উঠতে পারে- আমরা এখানে সেই পরিবেশ
সৃষ্টি করতে চাই। কাজেই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রাণহীন, কৃত্রিম,
গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি সর্বাঙ্গীণ জীবন-পরিবেশ।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের ষাটের
দশকের সাহিত্য আন্দোলনে অবদান
ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন
হয়, তিনি ছিলেন তার নেতৃত্বে। সাহিত্য
পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনার মাধ্যমে সেকালের নবীন সাহিত্যযাত্রাকে তিনি
নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সংহত ও বেগবান করে রেখেছিলেন এক দশক ধরে। 'কণ্ঠস্বর'
আন্দোলন ছিল একটি শিল্প-আন্দোলনের
নাম। দল, মত, বিশ্বাস বা আদর্শের জাতপাতের তোয়াক্কা তার ছিল না। লেখর
বিষয় বা বক্তব্য নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না তাঁদের। তাঁদের চাহিদা ছিল একটাই-
ন্যূনতম শিল্পশক্তির পরিচয় দিতেই হবে লেখায়, তাহলেই লেখা প্রকাশিত হবে। ওটি ছাড়া আর কিছু দিয়েই এ শিকে
ছিঁড়বে না। হ্যাঁ, সেইসঙ্গে ছিল আরেকটা শর্ত : তরুণ
হতেই হবে তোমাকে। তোমাকে হতে হবে জেদি, টাটকা, তাজা তরুণ- একরোখা, রাগি,
অসন্তুষ্ট তরুণ। হ্যাঁ, রাগি। কেননা রাগ না থাকলে প্রতিষ্ঠিতদের অচলায়তন ভেঙে নতুন
পথ সৃষ্টির বল্গাহীন উল্লাস কোথা থেকে অনুভব করবে রক্তের ভেতর? কী করে চারপাশের ভণ্ডামির ডেরাকে ছিন্নভিন্ন করবে?
ষাটের দশকে আমাদের সমাজে অবক্ষয় এসেছিল দুটি পর্যায়ে।
প্রথম ঢেউটি এসেছিল শ্বাস-চেপে-ধরা সামরিক নিগ্রহকে আশ্রয় করে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২-র
মধ্যে ঘটেছিল মূল ঘটনাটি,
যদিও এর জের চলেছিল একাত্তর অব্দি।
কেবল একাত্তর কেন, পরবর্তীকালের সব সামরিক ও সামরিকতা
সমর্থিত গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারের হাত ধরে এই ধারা জাতীয় জীবনকে ক্রমবর্ধমানভাবে
অধিকার করে নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। আজও তার গ্লানি জাতীয় জীবনকে
আবিল করে রেখেছে।
এর পরেরটা এসেছিল এর ঠিক পরপরই, বাষট্টি-তেষট্টির দিকে। এটা এসেছিল সামরিক স্বৈরশাসনের
উপতাত হিসেবে। সামরিক শাসনের দম-আটকানো ও নিরানন্দ পরিবেশকে আইয়ুব খান পুষিয়ে দিতে
চেয়েছিলেন সমাজজীবনে অবাধ ও জবাবদিহিহীন বিত্তের সচ্ছল ও কল্লোলিত স্রোতধারা বইয়ে
দিয়ে। অর্থ সংগ্রহের জন্য উন্নত দেশগুলোর দরজায় দরজায় ধরনা দিয়ে দেশের জন্য বিপুল
পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন তিনি। হঠাৎ-আসা সেই সুলভ বিপুল ও
অনোপার্জিত বিত্ত সমাজ জীবনের বন্দরে-বন্দরে রজতধারার সচ্ছল ঢেউ জাগিয়ে তোলে।
ষাটের দশকের শুরুতে আমাদের জাতীয় জীবনে যে অবক্ষয়
শুরু হয়, এই তরুণ-লেখকদের চেতনা জগতে তা
প্রথম সাড়া তোলে। কিন্তু কোনো নতুন চেতনাকে কেবলমাত্র অনুভব করার ভেতরেই একজন
লেখকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না,
ঐ চিত্রকে শৈল্পিক পরিপূর্ণতা
দেবার প্রয়োজনে এর বাস্তবতার ভেতর তাকে আমুণ্ডুপদনখ ডুবে যেতে হয়; আপেলের মতো রক্তিম সজীব ভাষায় ঐ অনুভূতিলোকের চিত্র
ভবীকালের জন্য এঁকে রেখে যেতে হয়। ষাটের ঐ তরুণদের মধ্যেও ছিল সেই চেষ্টা। এই
ভূমিকা ঠিকমতো পালনের মধ্যদিয়ে নিজেদের অজান্তে লেখকেরা একটি বড় ঐতিহাসিক দায়িত্ব
পালন করে বসেন। এর ভেতর দিয়েই তাঁরা হয়ে ওঠেন সমাজবাস্তবতা পরিবর্তনের শক্তিশালী
অচেতন হাতিয়ার। রাজনীতিবিদদের কাজ শুরু হয় এর পরে। শিল্পীদের এঁকে যাওয়া সমাজের
জীবনের ঐসব বেদনাদীর্ণ চিত্র থেকে সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা টের পেয়ে তাঁদের কাজ হয়
ঐ দুঃখময় সমাজ বাস্তবতাকে পাল্টে সমৃদ্ধিমুখী উচ্চতর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য
বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া।
ভালো লেখকদের একটা দল এই সময় দেখা দিয়েছিল আমাদের
সাহিত্যের অঙ্গনে, যাঁরা একটা জলবহুল মেঘের মতো এই
সাহিত্যের আকাশে দাঁড়িয়ে এর অঙ্গনকে খরা আর অনাবৃস্টি থেকে বেশ কিছুদিন বাঁচিয়েছে
এবং নিজেদের শ্রম, চেষ্টা এবং চরিত্র দিয়ে এই
সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কিছু উপহার দিয়েছে যা এর ধারাকে সজীব ও বহমান থাকতে সাহায্য
করেছে।
উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার
বাংলাদেশে টেলিভিশনের সূচনালগ্ন থেকে মনস্বী, রুচিমান ও বিনোদন-সক্ষম ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভুত হন
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। টেলিভিশনের বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় তিনি
পথিকৃৎ ও অন্যতম সফল ব্যক্তিত্ব। টিভি-উপস্থাপনায় জড়িত হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস। হঠাৎ একদিন মুস্তফা মনোয়ার আর
জামান আলী খান (পাকিস্তান টেলিভিশনের কর্মকর্তা)) আমার ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল
কলেজের (বিজ্ঞান কলেজ) হোস্টেলের কক্ষে এসে হাজির। তাদের অনুরোধ : কবি
জসীমউদ্দীনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। রাজি হয়ে গেলাম। টিভিতে সেই আমার প্রথম আসা।
পরবর্তীকালে কুইজ প্রোগ্রাম,
শিশুদের প্রোগ্রাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার ভেতর দিয়ে টিভির সঙ্গে
ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছি। তবে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত টিভির সাথে পুরোপুরি জড়িত
ছিলাম।'
একটি সাক্ষাৎকারে জানতে চাওয়া হয়েছিল, একজন উপস্থাপকের কী কী গুণ আবশ্যক বলে মনে করেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'উপস্থাপক ঠিক ঘোষক নন, উপস্থাপনা হল উজ্জ্বল উৎকর্ষময় ব্যক্তিত্বের একধরনের
বর্ণোজ্জ্বল প্রকাশ। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেউ ভালো উপস্থাপক হতে পারে
না। এটাকে দক্ষতা ভাবলে ভুল হবে। একজন উপস্থাপকের ব্যক্তিত্ব হতে হবে রুচিশীল, সপ্রাণ,
সপ্রতিভ, হাস্যময় ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর স্বভাবের মধ্যে একধরনের সারল্য
থাকতে হবে; যা দিয়ে তিনি দর্শকদের আপন করে
নেবেন। মনে রাখতে হবে যিনি দর্শকদের ড্রইংরুমে গিয়ে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলেন, তাঁকে কোনোমতেই কৃত্রিম বা আড়ষ্ট হলে চলবে না। এই জিনিসগুলো
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখানো কঠিন। খানিকটা জন্মগতভাবে, খানিকটা শিক্ষা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ থেকেই একজন উপস্থাপক এগুলো পেতে পারেন। অবশ্য অনেক
জিনিশ, যেমন উচ্চারণ, উপস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এমনি আরো অনেক কিছু প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া
যেতে পারে।'
উপস্থাপক হিসেবে আপনার দর্শকদের কাছে এত গ্রহণযোগ্য
হওয়ার কারণ কী? প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমি যখন ক্লাসের ছাত্রদের পড়াই তখন আমার মনের কথাগুলো
এমনভাবে বলার চেষ্টা করি,
যাতে ক্লাসের সবচেয়ে মধোহীন এবং
বোকা ছাত্রটিও তা বুঝতে পারে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি কতটা সহজে, স্বচ্ছন্দে ও হাস্যপরিহাসের মধ্যদিয়ে সরল ভাষায় তার হৃদয়ের
কাছে পৌছানো যায়। এতে সাধারণ ছেলেরাও যেমন আমার কথা বুঝতে পারবে তেমনি ভালো
ছেলেদের বোঝার পথেও কোনো বাধা থাকবে না। টেলিভিশনেও আমি অমনটাই করি। দর্শকদের কাছে
গভীর কিছু হুলে ধরতে চাইলেও তার উপস্থাপনা করি রম্য উপভোগ্য ও সহজ ভঙ্গিতে। আমার
বলার বিষয় যতই গভীর হোক-না কেন,
আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি, যাতে সবচেয়ে সাধারণ দর্শকটিও তা বুঝতে পারে। এর ফলে লাভ হয়
দুটো। সাধারণ দর্শকের কাছেও আমার বক্তব্য কমবেশি পৌছে যায়। আর বুদ্ধিমান, শিক্ষিত দর্শকেরা তো নিজগুণেই তা বুঝে নিতে পারেন।'
লেখক আবদুল্লাহ আবু
সায়ীদ স্যার
এইসব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট।
কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প,
নাটক, অনুবাদ,
জার্নাল, জীবনীমূলক বই ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর প্রস্থভাণ্ডারও যথেষ্ট
সমৃদ্ধ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ২৭টি।
এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আবু সাঈদ নিজেই বলেছেন, 'লিখতে চেয়েছিলাম। লিখতে পারিনি। মনে হয় লেখক হয়েই
জন্মেছিলাম। সেটা পূর্ণ করতে পারলাম না। এখনো আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কোটি-কোটি
জীবন্ত শব্দের গনগনানি। ইদানীং কিছু কিছু লিখছি। যদি আর-কিছুদিন বেঁচে যাই, তাহলে হয়তো কিছু লিখতে চেষ্টা করব।'
পরিবেশ ও সুশীল সমাজ আন্দোলন
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এতসব অবদান ছাড়াও সামাজিক
আন্দোলনে উদ্যোগী ভূমিকার জন্য তিনি দেশব্যাপী-অভিনন্দিত হয়েছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধ
আন্দোলন, পরিবেশ দূষণ-বিরোধী আন্দোলনসহ
নানান সামাজিক আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে প্রাণ পেয়েছে।
ছাত্রদের প্রতি অনুভূতি
একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে 'স্যার'
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক
শিষ্যদের কাছে মুর্শিদ যেমন শিক্ষকও তার কাছে তেমনি। তার আশ্রয়, উদ্ধার,
পথনির্দেশদাতা এবং তার মনোজগতের
চিরন্তনতার প্রতীক। চারপাশের সবকিছুর মধ্যেই ঐ সময় সে তার ঐ আকাঙ্ক্ষিত ধ্রুবকে
প্রত্যাশা করে, শিক্ষকের কাছে এই দাবি তার সবচেয়ে
বেশি। শিক্ষককে সে একটা অবিচল অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসেবে দেখতে চায়, এতে তার আত্মায় জোর আসে।
তিনি বলেন, 'ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা ভারি অদ্ভুত। যেমন স্নিগ্ধ আর পবিত্র, তেমনি মধুর আর চিরদিনের। একবার ছাত্র মানে চিরদিনের জন্যে
ছাত্র, একবার শিক্ষক মানেও চিরকালের জন্যে
শিক্ষক। এই সম্পর্কের কোনোদিন মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ছাত্র-শিক্ষকের
দেখা হোক না কেন, সেই মুহূর্তটিতে তারা দুজন দুজনের
কাছে প্রথমদিনের মতোই উজ্জ্বল আর আলোময়। একজন সত্যিকার শিক্ষকের কাছে ছাত্র তাঁর
আত্মার সন্তান। অচেনা, অপরিচিত, রক্ত সম্পর্কহীন দূরদূরান্ত থেকে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে
তাঁরই জীবন শোষণ করে বেড়ে ওঠা তারই অনিবার্য উত্তরাধিকারী। এই ছাত্রই তো তাঁর
সম্ভাবনা, বিকাশ, পরিণতি;
তাঁর জীবন, জীবনের অর্থময়তা; জন্ম এবং জন্মান্তর। তবু এটা ঠিক যে শিক্ষক এবং ছাত্রের অবস্থান এক নয়। কী করে
যেন আমরা শিক্ষকেরা তাদের চিনে ফেলি। তাদের সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা
টের পাই। এই চেনা জীবনের এক গভীর তলের চেনা। এই চেনা রহস্যময় আর অলীক। কেবল
মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে এর পরিমাপ করা কঠিন।'
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের
শিক্ষকতার টুকিটাকি
সায়ীদ স্যার তাঁর শিক্ষক জীবনে কখোনোই রোলকল করতেন
না। এর প্রথম কারণ হচ্ছে তাঁর ক্লাশে ছাত্রদের উপস্থিতি থাকতো সর্বোচ্চ সংখ্যায়।
অনেক সময় অন্যান্য ক্লাশের ছাত্রেরাও এসে জড়ো হত। শহরের নানান কলেজ থেকেও যেসব
ছাত্রেরা এসে ভিড় করত তার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তিনি ক্লাশের কথাবার্তার ভেতর
কবিতা, দার্শনিকতা এবং নির্মল কৌতুকের
সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। আজীবন প্রায় ছোটখাটো একটা জনতাকে পড়িয়েছেন। রোলকলকে তার
কাছে মনে হতো সময়ের অপব্যয়। তাই বছরের পয়লা ক্লসেই ঘোষণা করে দিতেন রোলকল না করার।
তিনি বলেন, 'অনিচ্ছুক হৃদয়কে ক্লাশে জোর করে
বসিয়ে রেখে কী করব? আমার চ্যালেঞ্জ ছিল এক ধাপ বেশি:
কেবল শিক্ষক হওয়া নয়, সব ছাত্রের হৃদয়ের কাছে পৌঁছানো, সব ছাত্রের হৃদয়কে আপ্লুত করা।' ক্লাশের সেরা ছাত্রটাকে পড়ানোর চেষ্টা করার চেয়ে তিনি পড়াতে
চেষ্টা করতেন ক্লাশের সবচেয়ে বোকা ছাত্রটাকে। সারাক্ষণ তাকেই বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কেননা তার বোঝা মানে ক্লাসের বাকি সবাইকে বোঝা ।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের
অধ্যাপনা জীবনের সমাপ্তি
১৯৬২ সালের পহেলা এপ্রিল তিনি রাজশাহী কলেজে শিক্ষক
পদে যোগ দিয়েছিলেন আর ১৯৯২ সালে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক পদটি যেদিন ছেড়ে দেন সেদিনও
ছিল পহেলা এপ্রিল। এটি তাঁর জীবনের একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য। শিক্ষাঙ্গণের অবক্ষয়, শিক্ষকদের ভেঙ্গে পড়া মূল্যবোধ তাঁকে বিদ্ধ করেছে সবসময়।
অপরিসীম ভালোবাসা, তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তি ও প্রজ্ঞা
মিশিয়ে তিনি অনুসন্ধান করেছেন এই অবক্ষয়ের কারণ। ছাত্রদের প্রকৃত আভিভাবক হিসাবে
জাতীয় এই দুর্যোগটির দিকে জাতির মনোযোগ ফেরাতে চেয়েছেন।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের পুরস্কার ও সম্মাননা
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এখানে
উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কারের কথা তুলে ধরা হলো : ১৯৭৭ সালে পেয়েছেন 'জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার' , ১৯৯৮ সালে পেয়েছেন মাহবুব উল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার; ১৯৯৯ সালে পান রোটারি সিড পুরস্কার; ২০০০ সালে পান বাংলাদেশ বুক ক্লাব পুরস্কার। ২০০৪ সালে
পেয়েছেন র্যামন ম্যাগস্যাসে পুরস্কার, ২০০৫ সালে পেয়েছেন একুশে পদক-২০০৫ এবং ২০০৮ সালে অর্জন করেন পরিবেশ পদক-২০০৮।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের বাবা নবম শ্রেণী থেকে দশম
শ্রেণীতে ওঠার সময় প্রথম হয়ে 'শেক্সপিয়ার-সমগ্র' বইটা পুরস্কার পেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ম্যাট্রিক
পরীক্ষা পাশের পর তাঁর বাবা বইটি তাঁর হাতে তুলে দেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে
তাঁর সখ্যতা সেখান থেকেই। একবার মুন্সীগঞ্জে কলেজের সেমিনারে তাঁর পিতা একটা
ইংরেজি প্রবন্ধ পড়েছিলেন নাম 'টিয়ারস অফ জেবুন্নেসা' (জেবুন্নেসার অশ্রু)। সেই লেখার ওপর জনাব সায়ীদের বক্তব্য
শ্রোতাদের বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। দিনকয়েক পর এক ভদ্রলোক তাঁর বাবার কাছে ঐ
বক্তৃতার উচ্ছসিত প্রশংসা করলে গর্বে তাঁর চোখ ছলছল হয়ে উঠেছিল। লাভ হিসাবে
অধ্যাপক সায়ীদের মাসিক হাতখরচের টাকা পদোন্নতি পেয়ে একলাফে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।
তিনি ষাটের দশকে দু'বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে
যোগদানের ডাক পেয়েছিলেন। প্রথমবারে ডেকেছিলেন সে সময়কার বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ
মুহম্মদ আবদুল হাই। দ্বিতীয়বার ১৯৬৮-৬৯-এর দিকে ডেকেছিলেন মুনীর চৌধুরী। তিনি তখন
বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। কিন্তু ঢাকা কলেজে প্রাণবন্ত, স্বপ্রতিভ,
উজ্জ্বল ছাত্রদের পড়ানোর তৃপ্তি, শিক্ষক-জীবনের অনির্বচনীয়তম আস্বাদ ছেড়ে তিনি যেতে চাননি।
তাঁর মতে, 'বাংলা বিভাগে যোগদান করাটা আমার
কাছে সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের ছেড়ে সবচেয়ে খারাপ ছাত্রদের পড়াতে যাওয়ার মত মনে হয়েছে।'
ঢাকা কলেজের শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ছেলেবেলায়,
স্কুল থেকে কলেজে উঠে, অর্থনীতির বইয়ে পড়েছিলাম কেন একজন শিল্পপতি, কন্ট্রাক্টর বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীর চেয়ে একজন
শিক্ষকের বেতন কম। যুক্তি হিসেবে সেখানে বলা ছিল একজন শিক্ষকের জীবন কাটে মার্জিত, পরিশীলিত পরিবেশে, বৈদগ্ধময় ব্যক্তিদের সাহচর্যে,
উচ্চতর জীবনচর্চার অবকাশময় আনন্দে।
জীবনের সেই মর্যাদা, তৃপ্তি বা শান্তি ঐ ব্যবসায়ী বা
নির্বাহীর জীবনে নেই। এই বাড়তি প্রাপ্তির মূল্য দিতে শিক্ষকের আয় তাদের তুলনায় হয়
কম। ঢাকা কলেজের শিক্ষকতায় ঐ তৃপ্তি আমার এত অপরিমেয় হয়েছিল যে কেবল বেতন কম হওয়া
নয়, আমার জন্য হয়ত বেতন না-থাকাই উচিত
হত। এই পাওয়া যে কতটা তা বুঝেছিলাম কিছুদিনের জন্য অন্য কালেজে গিয়ে।'
অধ্যাপক সায়ীদের সারাজীবনের পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি। এ
প্রসঙ্গে তিনি মজা করে বলেন,
"অনেকদিন
একটানা পরার ফলে পোশাকটা আমার চেহারার সঙ্গে এমন একাকার হয়ে গেছে যে আজ অনেকেরই
হয়ত সন্দেহ হয় যে ঐ পোশাক-পরা অবস্থায় আমি এই পৃথিবীতে জন্মেছিলাম কিনা। আমার
ছাত্রেরা আমার এই পোশাক দেখে সারাজীবনই অবাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে : 'আপনি কি সারাজীবনই পাজামা- পাঞ্জাবি পরেছেন?' 'হ্যাঁ।'
'আর কোনো
পোশাকই পরেননি? প্যান্ট-শার্ট-স্যুট কিছুই না?' 'না।'
'বিদেশে
গিয়েও না?' এমনি অসংখ্য প্রশ্ন। বাইরের
মানুষদের প্রশ্নও কম শুনতে হয়নি। আমি পাজামা- পাঞ্জাবি ধরেছিলাম কলেজে ওঠার সঙ্গে
সঙ্গে। ধরেছিলাম অবশ্য ঝোঁকের মাথায়। তবে এখন সরল জীবনের মতো আমার কাছে সরল পোশাকই
ভালো লাগে। কিন্তু পাঞ্জাবি ছাড়া কখনো আমি যে সারাজীবন আর কিছু পরতে পারিনি তার
কারণও আমার এই শিক্ষক জীবন।"
একটি বইয়ে আমি লিখেছি: ‘আমার জীবনে সবকিছুই এসেছে
দেরি করে। শৈশব এসেছে দেরি করে, কৈশোর এসেছে দেরি করে, যৌবন এসেছে দেরি করে, প্রৌঢ়ত্ব এসেছে দেরি করে। কাজেই
বার্ধক্যকে যদি আসতেই হয়, তবে তাকে আমার মৃত্যুর পরেই আসতে হবে।’
চৌকস মানুষেরা যে রকম, আমি ঠিক সে রকম নই। সামান্য জিনিস
বুঝতেও আমার সময় লাগে। প্রতিভাধর মানুষদের মতো ভূমিষ্ঠ হয়েই আমি বই পড়তে শুরু
করিনি। এ শুরু হয়েছে অনেক পরে, আমার কলেজজীবনে। স্কুলে পড়ার সময় আমার বড় বোন পাবনায়
অন্নদাশঙ্কর পাবলিক লাইব্রেরির সদস্য ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে সেখান থেকে তাঁর জন্য
দুটো করে উপন্যাস নিয়ে আসতাম।
প্রথম শৈশবে এটুকুই বইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। বোনের
ওই বইগুলো আমাকে পড়তে দেওয়া হতো না। সেসব ছিল মূলত উপন্যাস। ওগুলোতে নাকি
নারী-পুরুষের কীসব রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার থাকে। পড়লে চরিত্র খারাপ হয়। বড়
আপার চরিত্র উন্নয়নে সেগুলো সম্ভবত খুবই সহায়ক ছিল। কারণ, তাঁকে সারা সপ্তাহ ধরে শুধু ওসব
বই-ই পড়তে দেখতাম।
বই আমি আগেও অনেকবার দেখেছি, তবে তা প্রথম কখন অনন্য মোহ
ছড়িয়ে আমার নজর কাড়ল, তার একটা স্মৃতি মনে পড়ছে। তখন আমি ফাইভে পড়ি। আব্বা খুবই
পড়াশোনা করতেন। দোতলার কোনায় ছিল তাঁর একান্ত পড়ার ঘর। আমরা প্রায় কেউ-ই সে
ঘরে যেতাম না। একদিন আব্বা আমাকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। ঘরে গেলে আব্বা আমাকে জীবন
সম্পর্কে বেশ কিছু ‘সারবান’ কথা বললেন। কিছু তার মনে আছে, কিছু নেই। তবে সেসব কথার চেয়ে যা
আমাকে সেদিন অনেক বেশি টেনেছিল তা হলো, তাঁর ঘরভর্তি বইয়ের বিশাল ভান্ডার।
ওই ঘরটা ছিল পাঁচ দেয়ালের। দেখলাম, সবগুলো দেয়ালে শেল্ফভর্তি
রংবেরঙের অজস্র বই। যেদিকে তাকাই শুধু বই। আমি তখন ছোট, তুচ্ছকেও সে বয়সে অসামান্য লাগে।
ঘরভর্তি ওই বিপুল বই আমাকে অভিভূত করে ফেলল। ঘরটা আমার চেয়ে অনেক বড়, তাই ওই হাজার কয়েক বইকেও আমার
কাছে প্রায় লক্ষ-কোটি বই বলেই যেন মনে হলো-যেন আমাকে ঘিরে বইয়ের একটা অন্তহীন
জগৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে।
মনে হয়, এই ঘটনাটা আমার শিশুমনকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। শৈশবে
গভীরভাবে যে স্বপ্ন মানুষ একবার দেখে, সারা জীবন তাকেই সে বড়ভাবে পুনর্গঠন করতে চায়। আমি যে
সারা জীবন শুধু দুনিয়া হাতড়ে রাশি রাশি বই সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি, সে হয়তো সেদিনের ওই বিশেষ মুহূর্তের
স্বপ্নটাকে বড়ভাবে ফিরে পাওয়ার জন্য।
দুই
ক্লাস নাইনে পাবনা জিলা স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুকাল
আগেই আমাদের স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক এসেছিলেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। থ্রি
পিস স্যুট আর জিন্নাহ ক্যাপ পরে এই বিশালদেহী হেডমাস্টার স্কুলের বারান্দা দিয়ে
নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াতেন। সেই যুগে তিনি বিলেতের এডিনবরায় এক বছরের জন্য পড়তে
গিয়েছিলেন। ক্লাসে এসে তিনি নাকি বলতেন, ‘আমি যদি তোমাদের একবার বিলেতের গল্প বলি, সে যে কত কথা! তা তোমরা ভাবতেও
পারবে না; বুঝতেও
পারবে না।’ কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
সে সময় এ দেশ থেকে খুব কম লোকেরই বিলেতে যাওয়ার
সৌভাগ্য হতো। বিলেতে গিয়ে সেই জৌলুশভরা সভ্যতার সঙ্গে আমাদের এই বিমর্ষ মলিন
দেশটার যে বিশাল পার্থক্য তাঁরা দেখতেন, তা দেখে সে দেশ সম্পর্কে এক অপার বিস্ময় ও উদ্বেলিত
শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁরা ফিরে আসতেন। পঞ্চাশের দশকে আমাদের এক লেখক বিলেত ঘুরে এসে
একটা বই লিখেছিলেন। নাম: বিলেত দেশটাও মাটির।
এমন অবিশ্বাস্য ব্রিটিশ জাতি যে দেশে বাস করে, সে দেশটা যে আমাদের মতোই কাদামাটির
হতে পারে, তা দেখে
তাঁরা অবাক হতেন।
সেই প্রধান শিক্ষকই হঠাৎ অ্যাসেম্বলিতে বলেছিলেন, ‘তোমরা আগামী মাস থেকে আর স্কুলের
বড় লাইব্রেরিটাতে আসবে না। প্রতিটি ক্লাসে আমি একটা করে ছোট্ট লাইব্রেরি করে
দিচ্ছি। সেখান থেকেই তোমরা প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে বই নেবে। তবে বই সবাইকেই নিতে
হবে। এ বাধ্যতামূলক।’
এটা হয়তো ছিল তাঁর বিলেতি পড়াশোনারই ফসল। তিনি
প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটা করে বাক্স বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে থাকত বই। বাক্সগুলো
ক্লাসের দেয়ালের সঙ্গে আটকানো। প্রতি শনিবারে ওখান থেকে আমাদের বই নিতে হতো।
ক্লাসটিচার বেতন নিতেন আর ক্লাস ক্যাপ্টেন বই দিত।
বই নেওয়া তিনি সবার জন্য কেন বাধ্যতামূলক করেছিলেন, তা নিয়ে পরে ভেবেছি। আমার ধারণা, তিনি ভেবেছিলেন, যে ছেলেটা বই নিচ্ছে, সে যদি না-ও পড়ে, তবু তার বাড়ির অন্যরা—বাবা-মা, ভাইবোন এমনকি বন্ধুরা হয়তো পড়বে।
আর দিনের পর দিন বাড়িতে বই গাধার মতো টানাটানি করতে করতে ছেলেটারও হয়তো এক সময়
মনে হতে পারে, কী এত
আনা-নেওয়া করি, দেখি না
একবার পাতা উল্টিয়ে।
এভাবে দু-চারটা বই সে হয়তো পড়েও ফেলতে পারে। আর
যারা পড়াবে, তারা তো
পড়বেই। মানব-বিকাশের ওপর বইয়ের প্রভাব কী, তা তিনি জানতেন। এর ফলে আমাদের
স্কুলের পরিবেশ কয়েক বছরের মধ্যে আশ্চর্যভাবে পাল্টে গেল। দেখা গেল সবাই ক্লাসে, টিফিনের সময়ে বই নিয়ে কথা বলে।
বইয়ের কোনো হাসির কথা উঠলে সবাই হো হো করে হাসে, কোনো দার্শনিক কথা উঠলে দার্শনিক
হয়ে যায়, কবিতার
কোনো লাইন বললে সবাই কবি। আমাদের পুরো স্কুলটাই একটা ইন্টেলেকচুয়াল স্কুল হয়ে
গেল। তার ফলও ফলতে লাগল।
গোটা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের ছাড়িয়ে
যাওয়ার পিপাসা জেগে উঠল। স্কুল থেকে প্রতিবছর ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করতে বা স্টার
পেতে লাগল। সাধারণ ফলাফল হয়ে উঠল অসম্ভব ভালো। স্যার ফজলে হাসান আবেদ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, জিয়া হায়দার—সবাই এই স্কুলের
প্রায় সে সময়কার ছাত্র। বই যে মানুষকে কীভাবে উজ্জীবিত সুতোয় গেঁথে দিতে পারে, এ দৃশ্য এই আমার প্রথম দেখা।
তিন
১৯৬৮ সালে আমি একটা পাঠচক্র শুরু করি। আমার তখন মনে
হয়েছিল, আমাদের
জাতির জ্ঞানের এলাকা একেবারেই নিঃস্ব। জাতির ভেতর জ্ঞান দরকার। ঢাকা কলেজের কিছু
মেধাবী ছেলেকে নিয়ে শুরু হয়েছিল পাঠচক্রটা। কিছুদিন চলেছিলও ওটা, কিন্তু উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের
ডামাডোলে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। সারা দেশে যে বিদ্রোহের ক্ষোভ প্রজ্বলিত হয়ে
উঠল, তার মুখে সেই পাঠচক্র যে কোথায়
ভেসে গেল, খুঁজেও
পেলাম না।
স্বাধীনতার পর মনে হলো সোনার বাংলা তো হয়েই গেছে, এখন লেপ মুড়ি দিয়ে একটা ভালোমতো
ঘুম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ১৯৭৮ সাল আসতে আসতে টের পেলাম, সোনার বাংলা বলে আসলে কিছু নেই।
ওটা একটা স্বপ্নের নাম। বাংলা আসলে মাটি আর কাদার। সবার শ্রম, চেষ্টা, সাধনা আর সংগ্রাম দিয়ে একে সোনায়
পরিণত করতে হয়।
তখন আবার নতুন করে শুরু হলো নতুন পাঠচক্র। এই পাঠচক্র
পাঁচ বছর চললে বুঝলাম, আমাদের
চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। বহুমুখী জ্ঞান ও জীবনচর্চার ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের মনের
অচিন্তিত বিকাশ ঘটেছে। বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষুরধার আর সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তারা। সেই পাঠচক্রে ২০ জন
ছেলেমেয়ে ছিল। তাদের প্রায় সবাই আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রের নেতৃত্বে।
মনে হলো, এই পথে আমরা স্বচ্ছন্দে এগোতে পারি। প্রথমেই মনে হলো, ছোট্ট পরিসরে যা সফল হলো, সারা দেশের সবখানে কেন তা সফল হবে
না। কেন নয় দেশের সব স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি পড়াশোনা আর
সংস্কৃতিচর্চার আনন্দময় উৎকর্ষ কেন্দ্র? এভাবেই যাত্রা শুরু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের।
মাত্র ৩৫ টাকায় ১০টি বই কিনে ১৯৭৮ সালে শুরু হয়েছিল
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। ১৫ জন সভ্য নিয়ে শুরু হওয়া বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আজ সভ্য
১৫ লাখ।
চার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নাম দেওয়ার পর তা নিয়ে আমি
হতাশায় ভুগেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমাদের কর্মকাণ্ড শুধু সাহিত্যচেতনার বিকাশ ঘটাবে—আমাদের
স্বপ্ন তো এমন ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ। টোটাল ম্যান। তবে
এ নিয়ে এখন আর দুঃখ করি না।
কেননা, আমরা কাজ করি মূলত তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়ে। সাহিত্যের
নন্দিত ও অনন্য বইগুলো পড়ে ফেলা এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য খুবই উপকারী। তাদের
আমরা পড়তে দিই তাদের মন ও বয়সের উপযোগী বড় বড় লেখকদের সেরা ও অনবদ্য বইগুলো।
এসব বইয়ের ভেতর ওই লেখকদের ভেতরকার স্বপ্ন, সৌন্দর্য, আলো, মূল্যবোধ—সবকিছু বিচূর্ণিত
অবস্থায় মণিমুক্তার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়েরা সেগুলো পড়লে সেই
জ্যোতির্ময় জিনিসগুলো তাদের ভেতর সরাসরি চলে আসে।
এতে তাদের জীবন পূর্ণ হয়, আলোকিত হয়। আর জীবনের বহুমুখী
বিকাশের কর্মসূচি একটু একটু করে আমরা তো গড়ে তুলেছি।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম কার্যালয় ছিল ঢাকা
কলেজের পেছনে, নায়েমে—তখনকার
শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের একটা ছোট্ট মিলনায়তনে। সেখান থেকে আমরা চলে যাই ৩৭
ইন্দিরা রোডে। সেটা ছিল একটা ভাড়া করা বাড়ি। বাড়িটা খুব সুন্দর। আমাদের বর্তমান
অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ওই সময় ছিলেন বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিব। তিনি
কোনো একটা তহবিল থেকে আমাদের পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছিলেন। ওই সহযোগিতা আমাদের সামনে
সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। বাড়িটা আমরা ভাড়া নিই ওই টাকা দিয়েই।
সেই বছরেই কেন্দ্রের ভবনের জমিটা আমরা পাই।
দিয়েছিলেন আবুল হাসনাত, ঢাকার প্রথম মেয়র। আমার সহপাঠী। তিনি পুরান ঢাকার লোক।
আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার মতো তাঁর হাতে তখন গোটা কয়েক বাড়ি ছিল।
বাড়ির জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে হেসে বললেন, ‘ক্যান, আমাগো কাছে ক্যান?’ কথাটা বলেছিলেন তিনি ছাত্র বয়সের
রাজনীতিতে আমাদের বিরুদ্ধ অবস্থানকে কটাক্ষ করে। আমি তাঁকে আমাদের স্বপ্নের
আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে বলি। তিনি বললেন, ‘বুঝছি বুঝছি, ওই যে প্যারিসে আছে না-শিল্পী-লেখক-বুদ্ধিজীবীগো ছোট ছোট
আখড়া। ওই সব বানাইবার প্ল্যান করছেন।’ দেখলাম, উনি আশ্চর্যভাবে ব্যাপারটা ধরে
ফেলেছেন।
পাঁচ
১৯৯২ সালে আমি চাকরি ছাড়ি। চাকরি ছাড়াটা শুধু
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্য কাজ করার তাগিদে নয়। চাকরি ছাড়ার আরেকটা কারণ ছিল, তা হলো শিক্ষকজীবন নিয়ে আমার
সুগভীর ব্যর্থতাবোধ। দেশে শিক্ষাব্যবস্থার পতন আমার মন ভেঙে দিয়েছিল। একটা বিরাট
স্বপ্ন নিয়ে আমি শিক্ষকতায় গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল বড় জীবনের স্বপ্নে উজ্জীবিত
করে ছাত্রদের আমি বড় করে তুলব। কিন্তু একসময় মনে হলো, দেশব্যাপী কোচিং, নোট, মুখস্থ আর পাঠ্যবই সমাকীর্ণ
অধঃপতিত শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর তার কোনো সম্ভাবনাই নেই।
আমি মনে করি না যিনি ভালো বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের
মুগ্ধ, বিস্মিত
আর হতবাক করেন, তিনিই
ভালো শিক্ষক। চাকরি হিসেবে শিক্ষকতা করলেও একজন ভালো শিক্ষক হয়ে যান না। আমার
ধারণা, পৃথিবীতে
একধরনের লোক আছেন, যাঁরা
স্বপ্ন দেখেন তাঁর চারপাশের মানুষেরা বড় হোক, সমৃদ্ধ হোক, পৃথিবীকে জয় করুক; তা এঁরা যে পেশার মানুষই হোন না
কেন। আসলে শিক্ষক এঁরাই।
আমি মনে করি আমার মধ্যেও শিক্ষকের এমনি একটা ছোট্ট
হৃদয় আছে। এটা আব্বার মধ্যেও দেখতাম। যখন দেখলাম এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমি
কাউকে কিছু দিতে পারব না, তখন আর অর্থহীনভাবে বসে সময় নষ্ট করিনি। জীবন তো পালিয়ে
যাচ্ছে।
সাফল্যে আমি বিশ্বাস করি না। সাফল্য একটা বৈষয়িক
বিষয়। এ একটা দক্ষতা। অনেক সময় চোর-ডাকাত-দুর্বৃত্তরাও জগতে সফল হয়। আমাদের
দেশের অধিকাংশ সফল মানুষই হয়তো তাই। সাফল্যে আগ্রহ না থাকায় জীবনে কোনো কিছু
নিয়ে বিমর্ষ বোধ করি না। আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন মানুষ। আমার আগ্রহ আনন্দে, কাজে, উদ্দীপনায়। কাজের নিজেরই একটা
দীপান্বিত আনন্দ-জগৎ আছে। আমি সেই আনন্দলোকের শিকারি।
সাফল্য হলে আশা বাড়ে, আশার সঙ্গে ভয়। আমার ওসব নিয়ে
মাথাব্যথা নেই। প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়ে আমি পরের দিনকে তৈরি করতে চেষ্টা করি।
কী করে বলব, এক বছর
পরে কী হবে? আমি তখন
থাকব কি না, তাই বা কে
জানে। আমি কেবল জানি, আজকের
কাজের মধ্য দিয়ে কাল তৈরি হচ্ছে। কালকের মধ্য দিয়ে পরশু। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
কোনো দিন এত বড় হবে, এ তো আমরা
কল্পনাও করিনি।
আমরা জনাকয় মানুষ একসঙ্গে হব, পড়ব, আনন্দে থাকব, বন্ধুত্বে সৌহার্দ্যে এক হয়ে বাস
করব, এই ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আর
ভালোবাসার উপজাত হিসেবে যদি এসব হয়ে থাকে, তবে মন্দটাই বা কী?
ছয়
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে আজও আমার কোনো পরিকল্পনা
নেই। যখন যে স্বপ্ন মনকে প্রজ্বলিত করে, তা করার দিকে এগিয়ে যাওয়াকেই করণীয় বলে ধরি। বহু ছেলেমেয়ে
এ পর্যন্ত এর সভ্য হয়েছে, এখানে পড়েছে, এতেই আমি খুশি। ভবিষ্যতে হয়তো আরও পড়বে। তাদের শুধু যে বই
পড়াচ্ছি, তা নয়; বহু জায়গায় সাংস্কৃতিক
কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাও আছে। ভবিষ্যতে এ আরও বাড়াব। সরকার এখন ভাবছে, কর্মসূচিটাকে সব জায়গায়-প্রতিটি
স্কুল-কলেজে কীভাবে সহজে স্বল্প ব্যয়ে চালু করা যায়। আমরা সেই ছকটা বানিয়ে
দিয়েছি, যাতে বই
বা মনন শিক্ষা জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে যায়।
একদিন দেশের প্রতিটি মানুষের হাতে বই পৌঁছেছে, কেন্দ্র নিয়ে এই আমার শেষ স্বপ্ন।
কেন্দ্রের পরিবেশে মানুষ হয়ে ছেলেমেয়েদের মন সুন্দর হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে, তাদের মনের জানালা খুলছে; বইগুলোর মধ্য দিয়ে একটা বড়
স্বপ্নের সামনে তারা দাঁড়াচ্ছে, বড় জায়গা থেকে জীবনকে দেখছে, এ আমার জীবনের একটা আনন্দ।
আমাদের বই তো পাঠ্যবই নয়। পাঠ্যবইয়ের উদ্দেশ্য
টাকা। ও দিয়ে গাড়িঘোড়ায় চড়া যায়, কিন্তু উচ্চতর জীবনকে স্পর্শ করা যায় না। আমাদের বইয়ের
স্পর্শে কচি বয়সে এই যে তাদের মধ্যে এত বড় বড় জিনিস জড়ো হচ্ছে, বড় স্বপ্নে তারা জেগে উঠছে, এতে ভালো কিছু না হয়ে কি পারে?
সাত
আমরা গড়ে উঠেছি প্রায় পুরোপুরি দেশের ভেতর
থেকে—সরকার, জনগণ আর
নানা প্রতিষ্ঠানের সমর্থন, সহযোগিতা ও ভালোবাসা নিয়ে। এর শিকড় বাংলার মাটির গভীরে
প্রোথিত। আমরা শুধু দিই, কারও কাছ থেকে কিছু নিই না। তাই দেশের মানুষ একে তাদের
নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে।
দেশের এক অন্ধকার পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা
আলোর কথা বলেছি। তাই এ প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে আমাদের এত কষ্ট গেছে। আমরা যদি উন্নত
হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুর
উন্নয়নের কথা বা দাতা সংস্থাদের এজেন্ডায় সুর মিলিয়ে কথা বলতাম, তবে হয়তো বন্যার তোড়ে সহযোগিতা
এসে যেত। কিন্তু আমরা বলেছি আলোকিত মানুষের কথা; যা না বুঝি নিজেরা, না বোঝাতে পারি অন্যদের।
তাই দারিদ্র্য ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমরা
অর্থবিত্তহীনভাবে শুধু ভালোবাসার জোরে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। যেখানে ১০ টাকা
দরকার, কষ্ট করে
তা করেছি এক টাকায়। টাকা ছিল না বলে আমাদের চরিত্র ছিল। বন্ধু ছিল। আমরা প্রায়ই
বলি, টাকা দিয়ে কী করা যায় তা
দেখিয়েছে অনেকে। কিন্তু ও ছাড়া কী করা যায়, তা দেখিয়েছি আমরা।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের বলেন “হে মানব জাতি তোমরা শোন… আমি ওপর থেকে কখনো কথা বলতে
চাইনি। আমার মধ্যে পিতৃ হৃদয় নাই, প্রবীণ মানুষের হৃদয় নাই। সনত্মানের হৃদয় নাই, আমার
মধ্যে একটা হৃদয়ই আছে। তা হলো বন্ধুর হৃদয়। আমি সব মানুষকে সমান মনে করি। আমি
কয়েকদিন আগে জন্মেছি বলে আরেকজন আমার চেয়ে ছোট, প্রকৃতির চক্রানেত্ম আমি একটু আগে পৃথিবীতে এসেছি, এজন্য
আমি একটা কিশোরের চেয়ে বড়, ৭০ বছর বয়সেও তা ভাবি না। আমার চেয়েও অনেক মেধাবী কিশোর
পৃথিবীতে আছে। আমার চেয়ে অনেক যোগ্য কিশোর পৃথিবীতে আছে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে
মানুষের একটাই সম্পর্ক আমি বুঝি- বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক।
আজ কিশোর-তরুণ জাতির হাল তো তাদের হাতেই আসবে। তখন তাদের এই
মূল্যবোধসম্পন্ন আর উচ্চায়ত হৃদয় কি একটা বড় বাংলাদেশ গড়ে তুলবে আবদুল্লাহ আবু
সায়ীদ স্যারের দেখানো আলোকিত মন ও আলোকরেখায়।
সানজিদা রুমি কর্তৃক গ্রথিত http://www.alokrekha.com
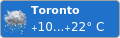



 লেখনীর সূত্রপাত শুরু এখান থেকে
লেখনীর সূত্রপাত শুরু এখান থেকে 



























স্যার অনেক শুভেচ্ছা জন্মদিনের । আলকরেখাকে সত্যি প্রশংসার যোগ্য , এমন আলোকিত ব্যক্তিকে নিয়ে লেখার জন্য
ReplyDeleteAlthough most mortgages are amortized over twenty five years, the average time to repay is approximately thirteen years. mortgage payment calculator canada RBC offers mortgage products for investment properties, vacation homes and additionally they offer rebates on home energy audits. mortgage payment calculator
ReplyDelete