চা শ্রমিকদের জীবন ও বাস্তবতা
সানজিদা রুমি
নদী
,পাথর, পাহাড়, জলপ্রপাত আর চা বাগানের কি অপূর্ব সমন্বয়! সিলেটের বর্ণনা দেওয়ার জন্য
এটাই যথেষ্ট। সিলেট মানেই যেন চা বাগান এবং চা বাগানের নারী শ্রমিকদের চা তোলার চিত্র।
সাজানো গোছানো চা বাগানের অবস্থানের কারণে সিলেটকে ‘দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির’ দেশ বলে থাকেন অনেকেই। ভাগ্যে জোটে ৮৫!
সাজানো গোছানো চা বাগানের অবস্থানের কারণে সিলেটকে ‘দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির’ দেশ বলে থাকেন অনেকেই। ভাগ্যে জোটে ৮৫!
পাহাড়ের
কোলে সবুজময় শতবর্ষী চা বাগানগুলোতে মৌসুমে চায়ের নতুন পাতার সূচনা হয়, কিন্তু সঙ্কট
মুক্ত হয় না নারী শ্রমিকদের জীবন।
চা বাগানের নারী শ্রমিকরা চা বাগানের অভ্যন্তরে ও বাইরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করলেও তারা জানে না নারী অধিকারের কথা। এসব নারী চা শ্রমিক এই শিল্পে অবদান রাখলেও তারা বরাবরই অধিকার থেকে বঞ্চিত।
চা বাগানের নারী শ্রমিকরা চা বাগানের অভ্যন্তরে ও বাইরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করলেও তারা জানে না নারী অধিকারের কথা। এসব নারী চা শ্রমিক এই শিল্পে অবদান রাখলেও তারা বরাবরই অধিকার থেকে বঞ্চিত।
নারী
চা শ্রমিকরা সকালে বাড়ির কাজ শেষ করে প্রতিদিন সকালে দলবেঁধে চা বাগানে চলে আসেন। সারাদিন
দাঁড়িয়ে চা তুলে সন্ধ্যায় ফিরে ৮৫ টাকার মালিক হন তারা। সমাজের সব পেশার নারীরা কমবেশি
সম্মান পেলেও চা শ্রমিক নারীরা আজীবন উপেক্ষিত। ন্যায্য মজুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা,
আবাসন, সুপেয় জল, স্যানিটেশনসহ কোনো কিছুরই সুবিধা পান না তারা। এক কথায় নারী হয়ে পাহাড়ের
কোলে জন্ম নেওয়াটাই তাদের অপরাধ। অথচ তারা চা শিল্পের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় কার্যকর ভূমিকা
পালন করছেন।
চা
শ্রমিকদের ২০০৭ সালে মজুরি ছিল ৩২ টাকা। ২০০৯ সালে ১৬ টাকা বাড়িয়ে করা হয় ৪৮ টাকা।
২০১৩ সালে বাড়ানো হয় ৬৯ টাকা, আর এখন ৮৫ টাকা। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি প্রতিদিন যেন
তাদের ২৫০-৩০০ টাকা পারিশ্রামিক দেওয়া হয়। বতর্মানে উত্সব ভাতা বেড়েছে। বৃদ্ধ চা শ্রমিকদের
সমাজসেবা মন্ত্রণালয় থেকে বছরে মাত্র ৫ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। সেটাও
চা শ্রমিকরা অনেক আন্দোলন করে আদায় করেছেন।
পাহাড়ের
কোলে জন্মের পর থেকেই চা বাগানে বসবাস মনিকা রাণীর। বয়স ৪২ বছর। নাম রাণী হলেও রাণীত্বের
কোনো ছোঁয়া নেই তার মাঝে। জেরিন চা বাগানে স্থায়ী চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তিনি।
কথা হলো তার সাথে। ১৫ বছর বয়স থেকে চা বাগানে কাজ করেন তিনি। তার মা মনা রাণীও ছিলেন
চা শ্রমিক। চা বাগানের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা খুব একটা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না, সুযোগ
না পাওয়ার দলে ছিলেন মণিকা রাণীও। বাংলা বর্ণমালা ছাড়া আর বেশিকিছু শেখার সৌভাগ্য হয়নি
তার। লেখাপড়া করার ইচ্ছে ছিল কি-না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ইচ্ছে তো ছিল।
কিন্তু অভাবের সংসার আর স্কুল দূরে হওয়ার কারণে পড়তে পারি নাই। লেখাপড়া করলে কি আর
আজ পোকার কামড় খেয়ে চা পাতা তুলতে হতো?’ মনিকা রাণী দৈনিক ২৩ কেজি চা পাতা তুলে আয়
করেন ৮৫ টাকা। নির্দিষ্ট পরিমাণে চা পাতা তুলতে না পারলে আয়ের পরিমাণও কমে যায়। তবে
ভালোভাবে সংসার চালানোর জন্য বাড়তি কাজ করে তিনি। বাড়তি কাজ করেও যেন সংসার চলে না
ঠিকমতো। সীমিত আয় ও জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে সংসার চালানো খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে মনিকা
রাণীর মতো হাজারো নারী চা শ্রমিকের। এই অর্থে কীভাবে সংসার চলে? জানতে চাইলে রাজ্যের
হতাশা ভর করলো মনিকা রাণীর মুখে। তিনি বলেন, ‘চলাই যায় না। আমি আর আমার স্বামী কাজ
করি, কিন্তু ঘরে ৬ জন নির্ভরশীল আছে। বর্তমানে যে রুজি পাই, তা দিয়ে কোনোমতেই চলে না।
আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ।’
মনিকা
রাণী কাছ থেকে জানা যায়, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নারী শ্রমিকরা পরিবারে জন্য খাবার প্রস্তুত
করেন। সকাল ৯টায় ঘর থেকে বের হয়। খাবার বলতে লাল চা, শুকনো রুটি। যে নারী শ্রমিকরা
চা বাগানে কাজে যান তারা সকালেই কিছু খাবার নিয়ে যান। দুপুরের সময় নারী শ্রমিকরা দলবেঁধে
বাগানের ভেতরে খাবারের জন্য বসে পড়েন। এ খাবারের মধ্যে রয়েছে কচি কুঁড়ি চা পাতা, আলু,
কাঁচা মরিচ ও মুড়ি।
খাতা-কলম
কেনার পয়সা কই
সুমি
রউতিয়া। ৩৯ বছর বয়সী এই শ্রমিকের গায়ের রঙ চিকচিকে কালো, চেহারায়ও হাড়খাটুনি পরিশ্রমের
ছাপ! তার দিকে তাকিয়ে যদি বয়স অনুমান করতে বলা হয় তাহলে যে কেউ বলবে বয়স ৬০-এর কম হবে
না। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলে উঠলেন, ‘খাইয়া, না খাইয়া কোনোমতে বাঁইচা আছি।
যতক্ষণ গতরে (গায়ে) শক্তি আছে ততোক্ষণ না হয় খাটলাম। অল্প একটু অসুস্থ হইলেই তো কাজ
করতে পারি না।’ সুমির দুই মেয়ে, এক ছেলে। তার স্বামী চা বাগানে কীটনাশক ছিটানোর কাজ
করেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করার বিষয়ে চানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘নিজে চলতে পারি না তবুও
পড়তে দিছি পোলা-মাইয়াগোরে। অনেকক্ষণ হেঁটে স্কুলে যায় তারা। পোলা-মাইয়া অনেক সময় স্কুলের
খাতা-কলম চায়, দিতে পারি না। ভালো-মন্দ খাইতি (খেতে) চায়, দিতে পারি না।
অসুস্থ
শরীর, নেই ডাক্তার
বাগান
এলাকায় সরকারিভাবে হাসপাতাল না থাকায় চা শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।
বাগান পরিচালিত স্বাস্থ্য বিভাগ থাকলেও এর পরিসেবা খুবই সীমিত। অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজ
করতে করতে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছেন সুমি রউতিয়া। ডাক্তার দেখাননি? এমন প্রশ্নের জবাবে
সুমি বলেন, ’ডাক্তার দেখাইমু কই! এখানে হাসপাতাল বলতে যা বুঝায় তা তো নাই। ডাক্তার
নাই, আছে মিডওয়াইফ। গেলে তো খালি প্যারাসিটামল ছাড়া আর কোনো ঔষধ দেয় না।’ প্যারাসিটামল
ছাড়া অন্য ঔষধের কথা বললে সরকারি হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলেন মিডওয়াইফরা। কিন্তু বলে
তো আর লাভ নেই তাদের, লাক্কাতুরা চা বাগান থেকে সরকারি হাসপাতালে যেতে আসতেই লেগে যায়
তাদের একদিনের মজুরি। তাই আর যাওয়া হয়ে ওঠে না সুমির মতো শত শত চা শ্রমিকের।
চুক্তি
আছে বাস্তবায়ন নেই
চা
শ্রমিকদের বসবাস খুবই অস্বাস্থ্যকর। চা বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া কুঁড়েঘরে চা শ্রমিকরা
একত্রে বসবাস করেন। প্রতিবছর শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের জন্য চুক্তিপত্র থাকলেও সেটা
বাস্তবে হয়ে ওঠে না। চা বাগান এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায়
চা শ্রমিকদের সন্তানরা অনেকেই শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
বাংলাদেশ
চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সিলেট বিভাগের ১৬২টি চা বাগানের রেজিস্টার্ড শ্রমিকের সংখ্যা
৮৯ হাজার ৮১২ জন। এর বাইরে অস্থায়ী (ক্যাজুয়েল) শ্রমিক আছেন আরো ১৯ হাজার ৫৯২ জন। অস্থায়ী
শ্রমিকরা রেশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড পান না। বসবাসের জন্য ১৬ হাজার পাকাঘর বরাদ্দ
আছে রেজিস্টার্ড শ্রমিকদের জন্য। আর প্রায় ৪৫ হাজার শ্রমিকের জন্য রয়েছে কাঁচাঘর। রেজিস্টার্ড
ও অস্থায়ী শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিকের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।
চা
বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাগান কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠিত স্কুল সংখ্যা ১১৮টি। স্কুলগুলোতে
২৫ হাজার ৯৬৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন মাত্র ৩৬৬ জন শিক্ষক। আর শিক্ষকরা অষ্টম থেকে
নবম শ্রেণি পাস। শ্রমিকদের কেউ যদি এসএসসি পাস করে থাকে তাহলে তাকে ‘বাবু’ বলা হয় এবং
তাকে বাগানে চাকরি দেওয়া হয়। তার বেতন আড়াই থেকে ৩ হাজার টাকার মধ্যেই থাকে। তবে এক্ষেত্রে
নারীদের সুযোগ নেই। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ৩টি বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য একজন মাত্র
এমবিবিএস চিকিত্সক ছিলেন। বর্তমানে ৬টি বাগানের জন্য একজন মাত্র এমবিবিএস চিকিত্সক
আছেন।
পরিত্যাক্ত
জমি নিজের শ্রম ঘাম দিয়ে আবাদ করে মূল্যবান চা উত্পাদন করে যাচ্ছেন চা শ্রমিকরা। তাদের
চা পৃথিবীর ২৫টি দেশে রফতানি করা হয়। কিন্তু চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার
সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান।
চা বাগানের প্রতিটি নারী শ্রমিকই চান, তারা নানা কষ্টে নিজেদের জীবনকে অতিবাহিত করলেও
তাদের সন্তানরা যাতে সুখ নামের সোনার হরিণটিকে ছুঁতে পারে। তারা লেখাপড়া করে মানুষের
মতো মানুষ হয়ে দেশের ভবিষ্যত্ উজ্জ্বল করতে পারে। কিন্তু চায়ের দেশে পর্যাপ্ত স্কুল
ও চা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার না থাকায় তাদের সেই স্বপ্ন বোধহয় চা বাগানের অন্ধকারে।
১৯২১
সালের ২০ মে চা
শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো মেঘনার ঘোলা জল।
২০ মে চা শ্রমিকদের
শোষণ-বঞ্চনা নিপীড়ন-নির্যাতন অধিকারহীন ও দাসত্বের শৃঙ্খল
থেকে মুক্ত হবার ঐতিহাসিক দিন।
১৮৫৪
সালে সিলেটের মালিনীছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠার
মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে
চায়ের আবাদ শুরু হয়। ব্রিটিশ
কোম্পানি একের পর এক
চা বাগান প্রতিষ্ঠা করলে প্রয়োজন হয়
শ্রমিক সংগ্রহের। ভারতের
আসাম, নাগাল্যান্ড, মধ্য প্রদেশ, উত্তর
প্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হাজার হাজার মানুষদের মিথ্যা স্বপ্ন ও উন্নত জীবনের
আশ্বাস দিয়ে এইসব চা
বাগানে নিয়ে আসা হয়। এসকল
মানুষেরা যেখানে এসেছিল একটু উন্নত জীবনের
স্বপ্ন নিয়ে সেখানে এসে
চিত্রপট দেখে সম্পূর্ণই ভিন্ন। কোম্পানি
মালিকরা এসকল শ্রমিকদের গহীন
জঙ্গল কেটে বাগান তৈরি
করার কাজে নিয়োজিত করে
নামেমাত্র মজুরিতে। সারাদিনের
হাড়ভাঙা খাটুনিতে একবেলা খাবারো জুটতোও না অনেক সময়। যার
ফলে অনাহারে অর্ধাহারে জীবন পার করতো
শ্রমিকরা। একদিকে
খাবার সঙ্কট, বাসস্থানের সঙ্কট অন্যদিকে বাগান মালিকদের নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে ওঠতে থাকে
চা বাগানে নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবন। এরকম
অসহনীয় পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে মালিক শ্রেণির
শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে
ফুঁসে ওঠে বিদ্রোহ ঘোষণা
করে চরাঞ্চলের চা শ্রমিকরা।
১৯২১ সালে ৩ মার্চ
নিজ মুল্লকে ফিরে যাবার জন্য
সিলেট ও তার আশপাশের
প্রায় ত্রিশ হাজার চা শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ
হয়ে বাগান ছেড়ে নিজ মুল্লুকে
ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু
করেন। “মুল্লক
চলো” অর্থাৎ নিজ ভূমিতে চলো। তাদের
দাবি ছিল ইংরেজদের অধীনে
কাজ করবে না ও
তাদের নিজেদের ভূমিতে ফিরে যাবে।
উল্লেখ্য, উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্বে
ছিলেন পন্ডিত দেওশরন এবং পন্ডিত গঙ্গা
দয়াল দীক্ষিত।
চা
শ্রমিকরা বুঝতে পারে চা বাগানের
মালিকেরা তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস ও উন্নত জীবনের
স্বপ্ন দেখিয়ে বন্দি করে রাখছে নিজেদের
স্বার্থ হাসিল করার জন্য।
তাই শ্রমিকরা তাদের পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে আগ্রহী
হয়ে ওঠে। কোনরূপ
চিন্তা-ভাবনা না করেই মাথা
গোঁজার ঠাই ছেড়ে বেরিয়ে
পরে রাস্তায়। কী
খাবে, কীভাবে যাবে এসব চিন্তা
একটি বারের জন্যেও তাদের সিদ্ধান্ত থেকে দূরে সরাতে
পারেনি। দলে
দলে শ্রমিকরা বলতে থাকে বার
বার মরার থেকে একবারেই
মরবো তবুও নিজ ভূমির
দিকে যাত্রা এগিয়ে যাবে। তারা
কেবল জানে চাঁদপুর জাহাজ
ঘাট। সেখানে
যেতে পারলেই জাহাজে চড়ে কলকাতায় ফিরে
যাবে। কিন্তু
জাহাজ ঘাট যাবে কি
করে? সবাই তখন জড়ো
হতে থাকে রেল স্টেশনে।
ফিনলে,
লিপটন, ডানকান ইত্যাদি নামি দামি ব্র্যান্ডের
যে চা খেয়ে আমরা
প্রতিদিন তাজা হই, সেই
চা উৎপাদন করতে গিয়ে চা
শ্রমিকরা প্রতিদিন আরো নির্জীব হয়।
চা
গাছ ছেটে ছেটে ২৬
ইঞ্চির বেশি বাড়তে দেয়
হয় না। চা
শ্রমিকের জীবনটাও ছেটে দেয়া চা
গাছের মতোই, লেবার লাইনের ২২২ বর্গফুটের একটা
কুড়ে ঘরে বন্দী।
মধ্যযুগের ভূমিদাসের মতোই চা মালিকের
বাগানের সাথে বাধা তার
নিয়তি।
তার
দৈনিক মজুরী মাত্র ৫৫ টাকা।
২০১১ সালে এর পরিমাণ
ছিল ৪৮ টাকা।
সাথে সপ্তাহে ৩ কেজি রেশনের
চাল ও আটা।
এ দিয়ে পরিবার নিয়ে
তিন বেলা খাবার জোটে
না।
সকালে
লবণ দিয়ে এক মগ
চা আর সাথে দুমুঠো
চাল ভাজা খেয়ে বাগানে
যেতে হয়, তার উৎপাদিত
চা ও দুধ চিনি
দিয়ে খাওয়ার সামর্থও তার নাই।
সারা দিন এক পায়ে
দাড়িয়ে, মাইলের পর মাইল হেটে
কঠোর পরিশ্রম। যারা
পাতা তোলেন, ২৩ কেজি পাতা
তুললেই কেবল দিনের নিরিখ
পূরণ হয়, হাজিরা হিসেবে
গণ্য হয়। গাছ
ছাটার কালে অন্তত ২৫০টা
গাছ ছাটতে হয় দিনে।
কিটনাশক ছিটালে অন্তত ১ একর জমিতে
কীটনাশক ছিটালেই তবে নিরিখ পূরণ। দুপুরে
এক ফাকে মরিচ আর
চা পাতার চাটনি, সাথে মাঝে মাঝে
মুড়ি, চানাচুর।
বাংলাদেশের
চা-শ্রমিকেরা বহুকাল ধরে নিরক্ষরতা, নিপীড়ন,
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার
মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে
আসছে। দেশের
মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। তারা
রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক,
মশা, সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে মাত্র ৬৯
টাকার বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা
অবধি কাজ করে, কোনো
কথা বলে না।
দেশের
অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় চা-শ্রমিকেরা সব
দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে
রয়েছে। এর
অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে নিরক্ষরতা। দেশে
বাজেটের একটা বিরাট অংশ
যেখানে ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা
খাতে, সেখানে চা-বাগানের শিক্ষার
হার অতি নগণ্য।
দেশের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য
চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন
কোটা-সুবিধা রয়েছে, চা-শ্রমিকদের সন্তানদের
জন্য তেমন কিছু নেই।
চা-বাগানগুলোতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা খুবই
নাজুক। অভিজ্ঞ
বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী না থাকায় চা-বাগানগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার খুব বেশি। ১৯৬২
সালের টি প্ল্যান্টেশন লেবার
অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৭ সালের
প্ল্যান্টেশন রুলসে চা-বাগানগুলোতে শ্রমিকদের
স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা মালিকের দায়িত্ব
থাকলেও তা প্রতিপালনের ব্যবস্থা
নেই। চা-শ্রমিকেরা ৮ বাই ১১
ফুট মাপের একটি ঘরে অন্তত
তিনটি প্রজন্ম বাস করে।
জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবাই প্রজাতন্ত্রের নাগরিক। এখানে
কোনো জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা চলবে না। চা-বাগানে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য
পর্যাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, কলেজ প্রতিষ্ঠা ও
চা-বাগানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাবৃত্তির
প্রচলন করা উচিত।
চা-বাগান এলাকায় পর্যাপ্ত সরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে চা-শ্রমিকদের বিশেষভাবে
গুরুত্ব দিতে হবে।
তাদের মানুষ মনে করলে এসব
অবশ্যই করতে হবে।
একেকদিন
হাত ফুলে যায়, পা
ফুলে যায়, ঝোপালো চা
গাছের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে
হাত পা কোমড় ছিলে
যায়। রোদে
পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সাপ বিচ্ছার
কামড় খেয়ে তারা বাগানে
কাজ করে। সন্তানের
শিক্ষা মেলে না, চিকিৎসা
মেলে না, যে ঘরটিতে
প্রজন্মান্তরে তার বসবাস সে
ঘরটিও তার হয় না,
ঘরটি ধরে রাখতে হলে
পরিবারের একজনকে অন্তত চা শ্রমিক হতেই
হয়।
অথচ
বাগান মালিকের জমি সরকারেরই খাস
জমি, সামান্য অর্থে লিজ নিয়ে সস্তায়
চা বাগান করে ফিনলে, ডানকান
ইত্যাদি ব্রিটিশ স্টারলিং কম্পানি, দেশীয় সরকারি এবং বেসরকারি কোম্পানি। ভর্তুকী
মূল্যে সার পায় তারা,
সহজ শর্তে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণও
বরাদ্দ বাগান মালিকদের জন্য। ফলে
মুনাফা তাদের কম নয়।
চট্টগ্রামের নিলাম হাউজে প্রতি কেজি চা যখন
১৪৭ টাকায় বিকোয়, তাদের খরচ তখন কেজি
প্রতি ৭০ থেকে ৮০
টাকা। ফলে
মুনাফ বিপুল।
অথচ
চা শ্রমিকদের দাবী সামান্যই- দৈনিক
মজুরী ১২০ টাকা(মালিকরা
মাত্র ৭ টাকা বাড়িয়ে
৫৫ টাকা থেকে ৬২
টাকা করতে চাচ্ছে), পরিবার
নিয়ে বসবাস করবার জন্য ৭৫০ বর্গফুটের
ঘর,বাগানে ভূমির অধিকার, সন্তানের শিক্ষা, পরিবারের সুষ্ঠু চিকিৎসা, চাকুরি স্থায়ী করণ ইত্যাদি। দিনে আট ঘণ্টা টানা কাজ করেও সকালে চা-পাতা ভাজা, দুপুরে শুকনা রুটি এবং রাতে মরিচ দিয়ে ভাত খেয়ে জীবন কাটাচ্ছেন সিলেটের শ্রীমঙ্গলের চা শ্রমিকরা। টানা আট ঘণ্টার প্রচণ্ড পরিশ্রম শেষে প্রতিদিন একজন শ্রমিক ২৩ কেজি চা-পাতা সংগ্রহের পরেও মজুরি হিসেবে পাচ্ছেন মাত্র ৮৫ টাকা।
এই টাকায় শ্রমিকরা না নিজে ভালোভাবে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারছেন, না তাদের সন্তানরা ভালোভাবে বেড়ে উঠছে। আর পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরাও অপুষ্টিতে ভুগছেন। বিট্রিশ আমলে চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল সর্বপ্রথম দৈনিক ২১ টাকা, পরবর্তীতে তা ২৮ টাকা, ৪৮ টাকা ও ৬৯ টাকা ও সর্বশেষ এসে এই মজুরি দাঁড়ায় ৮৫ টাকায়। চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা ও চা শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে নানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাম ভজন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, চা শ্রমিকদের বেতন কাঠামো অত্যন্ত অমানবিক। এই বেতন দিয়ে তারা ধুঁকছে কিন্তু একে বেঁচে থাকা বলে না। তবে আমরা এ নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষিতে যাচ্ছি। শিগগিরই সর্বনিম্ন ৪ জন সদস্যের একটি পরিবারের জীবনের ব্যয়ভারের কথা চিন্তা করে ২৩০ টাকা মজুরি ধরে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানাতে যাচ্ছি। সিলেটের গান্ধিছড়া চা বাগান সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, চা বাগানের কাজের পাশাপাশি বাড়তি রোজগারের জন্য শ্রমিকদের অন্য কাজও করতে হচ্ছে। শ্রমিকরা জানান, শুধু চা বাগানে কাজ করে তাদের চলে না। বেঁচে থাকার তাগিদে চা শ্রমিকরা রাবার বাগানের কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করছেন। এক আঁটি রাবার কাঠ বিক্রি করে তারা মাত্র ২০ টাকা পান। কিন্তু নির্দিষ্ট কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা কাঠ সংগ্রহের সুযোগ পান না। এ ছাড়া টাকা জমিয়ে এখন কেউ কেউ গরু-ছাগলও পালন করেন। জানা যায়, গান্ধিছড়া গ্রামে মোট ৩৭৪ জন শ্রমিক আছেন। আট বাই আটের একটি ঘরে দুটি করে রুম। এর এক কোনে রান্নাঘর। এর মধ্যেই গাদাগাদি করে থাকছেন সাত-আট সদস্যের এক-একটি পরিবার। এই শ্রমিকরা জানান, তারা সকালে শুকনা মরিচ দিয়ে, চা-পাতা ভাজা খেয়ে কাজে যান। দুপুরে খান শুকনা রুটি। আর দিন-রাতে মাত্র একবেলা ভাত খাওয়ার সুযোগ পান। কখনো টাকা না থাকলে ভাতও খেতে পারেন না। দিন শেষে একজন চা শ্রমিক ৮৫ টাকার মধ্যে ৩৫ টাকা দিয়ে দুই কেজি চাল, ১০ টাকা দিয়ে ১০০ গ্রাম মসুর ডাল, ১০ টাকার হলুদ-মরিচ ক্রয় করেন। বাকি ৩০ টাকা তেল, নুন বা অন্য কিছুতে খরচ হয়। শ্রমিকরা জানান, তারা দুই সপ্তাহে একবার বাজারের সবচেয়ে কম দামি সিলভারকার্প মাছ কিনে খাওয়ার সুযোগ পান। মাসে একবার বাসায় মেহমান আসলে চা শ্রমিকরা তাদের ঘরের মোরগ-মুরগি খাওয়ান। কিন্তু এটিও তাদের জন্য বিলাসিতা। শ্রমিকরা বলেন, ‘কষ্টের জীবন হলেও আমরা চুরি করি না। সত্ভাবে জীবন কাটাই। ’ শ্রমিকরা জানান, এই বাগানগুলোতে তারা সকাল ৮টা থেকে শুরু করে বিকাল ৪টা পর্যন্ত টানা কাজ করেন। আর আট ঘণ্টা কাজ করার পর প্রতিদিন একজন শ্রমিককে ২৩ কেজি চা-পাতা সংগ্রহ করতে হয়। এর পরেই তাকে ৮৫ টাকা মজুরি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ২৩ কেজির ওপর প্রতি কেজি বাড়তি চা পাতার জন্য একজন শ্রমিক সাড়ে তিন টাকা করে পান। আর যদি পাতা ২০ কেজির কম হয় তাহলে আশি টাকার কম করে মজুরি দেওয়া হয়। আবার কিছু বাগানে দিনে ২৩ কেজি করে চা-পাতা সংগ্রহের কথা থাকলেও শ্রমিকদের দিয়ে ২৪ কেজি করে পাতা সংগ্রহের বিনিময়ে মজুরি দেওয়া হচ্ছে। সন্ধ্যা রানী নামে এক শ্রমিক বলেন, আমাদের টানা আট ঘণ্টা কাজ করে যেতে হয়। এর মধ্যে একদিন পানি খেয়ে আমার আরেক বোন একটু সুপারি খাওয়ার অনুমতি চাইতেই সার্দার তাকে নেতিবাচক কথা বলেন। বিনতী দাস নামের সেই চা শ্রমিককে সুরেন্দ্র সর্দার সুপারি খাওয়ার অপরাধে অশ্রাব্য কথা বলেন। চা গাছ ছেঁটে ২৬ ইঞ্চির বেশি বাড়তে দেয়া হয় না। চা শ্রমিকের জীবনও যেন চা গাছের মতোই। লেবার লাইনের ২২২ বর্গফুটের কুড়ে ঘরে বন্দী। সারাদিন দাঁড়িয়ে কাজ করে মজুরি পান মাত্র ৬৯ টাকা। ঠিকভাবে মেলে না সন্তানের শিক্ষা। নেই চিকিত্সার ভালো ব্যবস্থা। আর বিনোদন সে তো সোনার হরিণ। এছাড়া পরিবারের একজন চা শ্রমিক না হলে বসত ঘরও হারাতে হয়।
দেশে এখন মোট চায়ের চাহিদা ৫ কোটি কেজি। ১৬৮টি বাগান থেকে আসে। প্রায় সাড়ে ৬ কোটি কেজি। তাই চাহিদা মিটিয়ে চা রফতানি করে বাংলাদেশ। দেশে উত্পাদিত চায়ের দাম বেশি- এই অজুহাতে গত বছর ভারত থেকে চা আমদানির অনুমতি দেয় সরকার। তবে ভারত থেকে আমদানি বন্ধ না হলে দেশের চা শিল্প সংকটে পড়তে পারে- এমন আশঙ্কা শিল্প মালিক-শ্রমিকদের। তাদের দাবি, নিম্নমানের ভারতীয় চা আসায় বাজার হারাচ্ছে দেশীয় চা। আর এই ধারা অব্যাহত থাকলে ১২ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়তে পারে।
হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ব্যবস্থাপক ইমদাদুল হক বলেন, দেশের এই শিল্পের সাথে জড়িত ১২ লাখ শ্রমিক। এমনিতেই সামাজিক অর্থনৈতিক নানা সূচকে পিছিয়ে চা বাগানের এই শ্রমিকরা। অন্য কোন কাজ না জানায় চা বাগানের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ নেই তাদের।
চা শ্রমিক নেতা কাঞ্চন পাত্র বলেন, ভারত থেকে সস্তা ও নিম্নমানের চা আমদানি অব্যাহত থাকলে, ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হবেন অনেক বাগান মালিক। আর তাতে হুমকির মুখে পড়বে শ্রমিকরা। বাড়তে পারে সামাজিক সংকট। তাই লাখো শ্রমিকের জীবন জীবিকা টিকিয়ে রাখতে চা আমদানির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।
চা শ্রমিকদের দিনকাল
শ্রম মন্ত্রণালয় তিন শ্রেণির চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৬৯, ৬৭ ও ৬৬ টাকা নির্ধারণ করেছে। আগে তাদের মজুরি ছিল যথাক্রমে ৬২, ৬০ ও ৫৯ টাকা। সঙ্গে সপ্তাহে ৩ কেজি রেশনের চাল ও আটা। এ দিয়ে পরিবার নিয়ে তিন বেলা খাবার জোটে না শ্রমিকদের। সকালে লবণ দিয়ে এক মগ চা আর সাথে দুমুঠো চাল ভাজা খেয়ে বাগানে যেতে হয়। অথচ বাগান মালিকের জমি সরকারেরই খাস জমি। সামান্য অর্থে লিজ নিয়ে বাগান করে বেসরকারি কোম্পানিগুলো। 'অল্প টাকা মজুরি পাই। এতে একজনেরই চলে না। ছেলে মেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে গেছে'- বলছিলেন চা শ্রমিক শিখা রবিদাস। চা বাগান ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপকালে অনেক শ্রমিক তাদের ক্ষোভের কথা জানান।
চা শ্রমিকদের ভাষার ব্যবহার দেখলে মনে হবে এখনও ব্রিটিশ শাসনামল চলছে। এই যেমন- ব্যবস্থাপককে ডাকে 'বড় বাবু' বলে। সহকারি ব্যবস্থাপককে 'ছোট বাবু' বলে ডাকে। এছাড়া ব্যবস্থাপকের বাসার কাজের লোকদের 'বেয়ারা' বলে ডাকা হয়। এছাড়া কেউ বেড়াতে গেলে তাদেরকে 'সাহেব' বলে চা শ্রমিকরা।
একটু পিছনে ফেরা
এই শিল্পটি স্থাপিত হয়েছিল বৃটিশ ঊপনিবেশিক সময়েই। পাহাড়ি জায়গা বেছে নেয়া হয় চা শিল্পের জন্য। শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় সমাজের সবচেয়ে নিচু শ্রেণির হরিজন, কোল, মুন্ডা, কৈরি, চন্ডাল, সাঁওতাল প্রভৃতি সমপ্রদায়ের লোকজনদের যাদের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি থাকলেও তা উপেক্ষিত। জানা গেছে, বৃটিশরা চা শ্রমিকদের মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ডের রাত্রি, ডোমকা, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এনেছিল। চা বাগান বানানো ছাড়া অন্য কোন কাজ জানা নেই এদের।
রক্তাক্ত ইতিহাস
বাংলাদেশে চা শিল্পের ইতিহাস ১৫০ বছরের। সিলেটে চা বাগান তৈরির শুরুর দিকে উন্নত জীবনযাপনের আশা নিয়ে জন্মমাটি ছেড়ে চা বাগানে কাজ করতে আসে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের অভাবী মানুষ। কিন্তু কাজে এসে তাদের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়। স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা নিয়ে তারা ফিরতে চায় নিজের দেশে। শ্রমিকরা দেশ ত্যাগ করতে গেলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নির্বিচারে হাজার হাজার চা শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। ১৯২১ সালের ২০ মের সেই রক্তাক্ত পরিণতিতে চা শ্রমিকদের দেশে ফেরার স্বপ্নও শেষ হয়ে যায়।
বাগানগুলোতে নেই কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। আধুনিক চিকিত্সা পদ্ধতির পরিবর্তে এখনও তারা অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর চিকিত্সা পদ্ধতি ব্যবহার করে। আর তাই চা বাগানের শত শত শিশু অপুষ্টির শিকার। তবে বর্তমানে চা বাগানগুলোতে হাসপাতাল থাকলেও সেখানে নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ দেয়া হয়। অন্যদিকে নারী শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটিও ঠিক ভাবে পায় না। জানা গেছে, এমনও হয়েছে কর্মস্থলেই অনেক বাচ্চার জন্ম হয়েছে। তবে কিছু বাগানে নারী শ্রমিকরা সরকারি আইন অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছে।
শিক্ষা ও বিনোদন ব্যবস্থা
সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী সকল চা বাগানে স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে। তবে সেটার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, অনেক চা বাগানে শিক্ষার আলো ছড়ানোর ব্যবস্থা নেই। আর যাও আছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (আইএলও) বিধান অনুযায়ী, ৮ ঘন্টা শ্রমের নিয়ম থাকলেও চা শ্রমিকদের কোন শ্রমঘন্টা নেই। আর বিনোদনের তো প্রশ্নই আসে না। চা শ্রমিকদের বিনোদন বলতে নেশায় বুদ হয়ে থাকা! তবে এখন অনেকে বিভিন্ন খেলাধুলা করে থাকে।
মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী চা বাগান
দিনটি ঐতিহাসিক ৪ এপ্রিল। ১৯৭১ সালের এই দিনে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানের বাংলোটিতে দেশ স্বাধীন করার জন্য ঐতিহাসিক এক শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ২৭ জন সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকেই সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তত্কালীন মেজর সি আর দত্ত, মেজর জিয়াউর রহমান, কর্নেল এম এ রব, ক্যাপ্টেন নাসিম, আব্দুল মতিন, মেজর খালেদ মোশাররফ, কমান্ডেন্ট মানিক চৌধুরী, ভারতের ব্রিগেডিয়ার শুভ্রমানিয়ম, মৌলানা আসাদ আলী, লে. সৈয়দ ইব্রাহীম, মেজর কে এম শফিউল্লাহ প্রমুখ।
তেলিয়াপাড়া চা বাগান ব্যবস্থাপকের বাংলোটিকে ৩ নম্বর সেক্টরের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বৈঠক শেষে এম.এ.জি ওসমানী নিজের পিস্তলের ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের শপথ করেন। বাংলোর সামনে একটি বুলেট স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।
এদিকে
চা করেরা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে রেল
কর্তৃপক্ষকে রেলের
টিকিট চা শ্রমিকদের না
দিতে নির্দেশ দেয়। অন্য
কোনো উপায় না দেখে
স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে রেলপথ ধরে
হাঁটতে থাকে চাঁদপুরের জাহাজ
ঘাটের উদ্দেশ্যে ।
কয়েকদিনের
হাঁটায় শ্রমিকরা যখন হবিগঞ্জ পৌঁছে
সিলেট থেকে তখন হবিগঞ্জের
তৎকালীন কংগ্রেস নেতা শিবেন্দ্র বিশ্বাস
এগিয়ে আসেন এবং তার
নেতৃত্বে তার কর্মীরা পথে
পথে শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ ও রাত্রি যাপনের
ব্যবস্থা করেন। স্থানীয়
স্বদেশী কর্মীরাও শ্রমিকদের সাথে যোগ দিয়ে
একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং শ্রমিকদের
মানসিক শক্তি ও সাহস যোগান। খাদ্য
ও পানির অভাবে পথে পথে মৃত্যু
হয় অনেক শ্রমিকের।
তবুও থেমে থাকেনি তাদের
মুল্লকে চলার সংগ্রাম ।
১৯২১
সালের ২০ মে শ্রমিকরা
গিয়ে পৌঁছে চাঁদপুর জাহাজ ঘাটে। অন্যদিকে
বাগান মালিকরা সরকারের সহযোগিতায় চা শ্রমিকদের প্রতিরোধ
করতে চাঁদপুর মেঘনাঘাটে আসাম রাইফেলস এর
গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করে। ঘাটে
জাহাজ যখন ভিড়লো শ্রমিকরা
তখন পাগল হয়ে জাহাজে
ওঠতে গেলে গুর্খা সৈন্যরা
বাধা দিতে থাকে এবং
তাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য
নির্বিচারে গুলি চালায়।
এতে শত শত শ্রমিক
মৃত্যুবরণ করে। শ্রমিকের
রক্তে লাল হয়ে উঠে
মেঘনার জল।
২০০৮
সাল থেকে দেশের ২৪১টি
চা বাগানের প্রায় প্রতিটি বাগানে অস্থায়ী বেদী নির্মাণ করে
চা শ্রমিকরা এই দিনটিকে চা
শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন
করে আসছে। চা
শ্রমিকদের দাবি এই দিবসটিকে
যেন সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।
ব্রিটিশ
উপনিবেশ, পাকিস্তান আমল ও স্বাধীনতার
৪৪ বছর পরও আজো
চা শ্রমিকরা নিম্ন মজুরি আর মানবেতর জীবন
যাপন করছে। আজো
দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি তাদের জীবন।
বাংলাদেশের
চা-শ্রমিকেরা বহুকাল ধরে নিরক্ষরতা, নিপীড়ন,
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার
মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে
আসছে। দেশের
মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। তারা
রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক,
মশা, সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে মাত্র ৬৯
টাকার বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করে, কোনো কথা বলেনা….
দেশের
অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় চা-শ্রমিকেরা সব
দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে
রয়েছে। এর
অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে নিরক্ষরতা। দেশে
বাজেটের একটা বিরাট অংশ
যেখানে ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা
খাতে, সেখানে চা-বাগানের শিক্ষার
হার অতি নগণ্য।
দেশের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য
চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন
কোটা-সুবিধা রয়েছে, চা-শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য তেমন কিছু নেই….
চা-বাগানগুলোতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা খুবই
নাজুক। অভিজ্ঞ
বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী না থাকায় চা-বাগানগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার খুব বেশি। ১৯৬২
সালের টি প্ল্যান্টেশন লেবার
অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৭ সালের
প্ল্যান্টেশন রুলসে চা-বাগানগুলোতে শ্রমিকদের
স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা মালিকের দায়িত্ব
থাকলেও তা প্রতিপালনের ব্যবস্থা
নেই। চা-শ্রমিকেরা ৮ বাই ১১
ফুট মাপের একটি ঘরে অন্তত
তিনটি প্রজন্ম বাস করে।
জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবাই প্রজাতন্ত্রের নাগরিক। এখানে
কোনো জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা চলবে না। চা-বাগানে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য
পর্যাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, কলেজ প্রতিষ্ঠা ও
চা-বাগানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাবৃত্তির
প্রচলন করা উচিত।
চা-বাগান এলাকায় পর্যাপ্ত সরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে চা-শ্রমিকদের বিশেষভাবে
গুরুত্ব দিতে হবে।
তাদের মানুষ মনে করলে এসব
অবশ্যই করতে হবে।
সানজিদা রুমি কর্তৃক গ্রথিত http://www.alokrekha.com
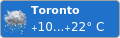






 লেখনীর সূত্রপাত শুরু এখান থেকে
লেখনীর সূত্রপাত শুরু এখান থেকে 





















চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনী নিয়ে লেখাটা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমরা কেবল বাইরের সৌন্দর্যটাই দেখতে পাই। তার পেছনে কত রূঢ় বাস্তবতা আর রক্তক্ষরণ তা আমরা ভাবি না। অনেক অনেক সাধুবাদ সানজিদা রুমিকে। এভাবেই আমাদের চোখের ও জ্ঞানের আলোয় আমরা আলোকিত হয় আলোকরেখায় এই কামনা করি।
ReplyDeleteসানজিদা রুমি কর্তৃক গৃহীত লেখাটি চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনী নিয়ে লেখাটা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম।কত রূঢ় বাস্তবতা আর রক্তক্ষরণ তা আমরা ভাবি না। অনেক অনেক সাধুবাদ সানজিদা রুমিকে। এভাবেই আমাদের চোখের ও জ্ঞানের আলোয় আমরা আলোকিত হয় আলোকরেখায় এই কামনা করি। অনেক ধন্যবাদ
ReplyDeleteবাংলাদেশের চা-শ্রমিকেরা বহুকাল ধরে নিরক্ষরতা, নিপীড়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে আসছে। দেশের মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই।
ReplyDeleteসানজিদা রুমি কর্তৃক গৃহীত লেখাটি চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনী নিয়ে লেখাটা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম।কত রূঢ় বাস্তবতা আর রক্তক্ষরণ তা আমরা ভাবি না। অনেক অনেক সাধুবাদ সানজিদা রুমিকে
ReplyDeleteচা শ্রমিকদের বসবাস খুবই অস্বাস্থ্যকর। চা বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া কুঁড়েঘরে চা শ্রমিকরা একত্রে বসবাস করেন। প্রতিবছর শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের জন্য চুক্তিপত্র থাকলেও সেটা বাস্তবে হয়ে ওঠে না। চা বাগান এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় চা শ্রমিকদের সন্তানরা অনেকেই শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
ReplyDeleteবাংলাদেশের চা-শ্রমিকেরা বহুকাল ধরে নিরক্ষরতা, নিপীড়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে আসছে। দেশের মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক, মশা, সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে মাত্র ৬৯ টাকার বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করে, কোনো কথা বলেনা….
ReplyDelete